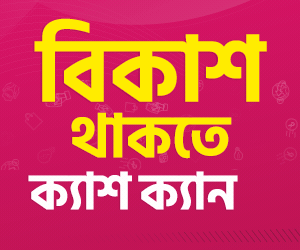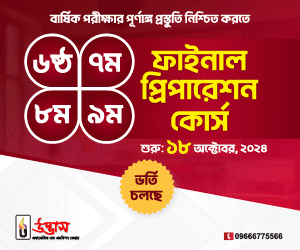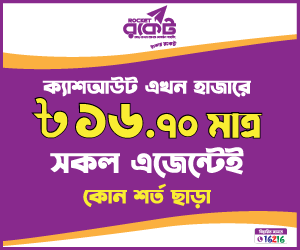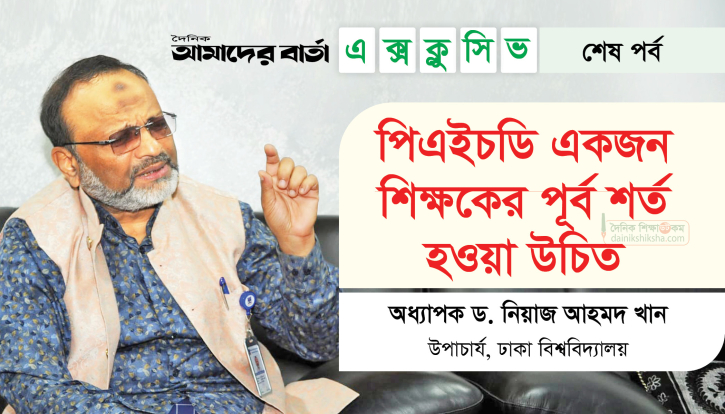
ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিজেই নিজের ক্ষমতা কমিয়ে ফেলার পক্ষে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। লাগাম টানতে টান অর্থ উত্তোলনের একক ক্ষমতায়। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নিরঙ্কুশতায়। কিন্তু, কেনো? দৈনিক আমাদেও বার্তাকে দেয়া সাম্প্রতিক এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে সাবলিলভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও কথা বলেছেন, সমসাময়িক পরিস্থিতি ও করণীয়, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, গবেষণার মান ও প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।
পিএইচডি রিসার্চ বর্তমানে খুব বেশি প্রচলিত একটা শব্দ। সম্প্রতি একটি কথা উঠেছে যে, ‘নো পিএইচডি নো প্রফেসর’। এই বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? অধ্যাপনার জন্য পিএইডডি কতোটা জরুরি বলে মনে করেন?
প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের নিয়োগ নিয়ে অনেকরকম সমালোচনা আছে, আমাদের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা পদ্ধতিগতভাবে রাজনীতিকরণ করেছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রাজনীতিকরণ করেছি। আমরা যারা রাজনীতির বাইরের মানুষ, আমাদের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন একটা সহনীয় পর্যায়ে আছে। এবং এটি করতে গেলে কিছু ভালো উদাহরণ তৈরি করতে হবে।
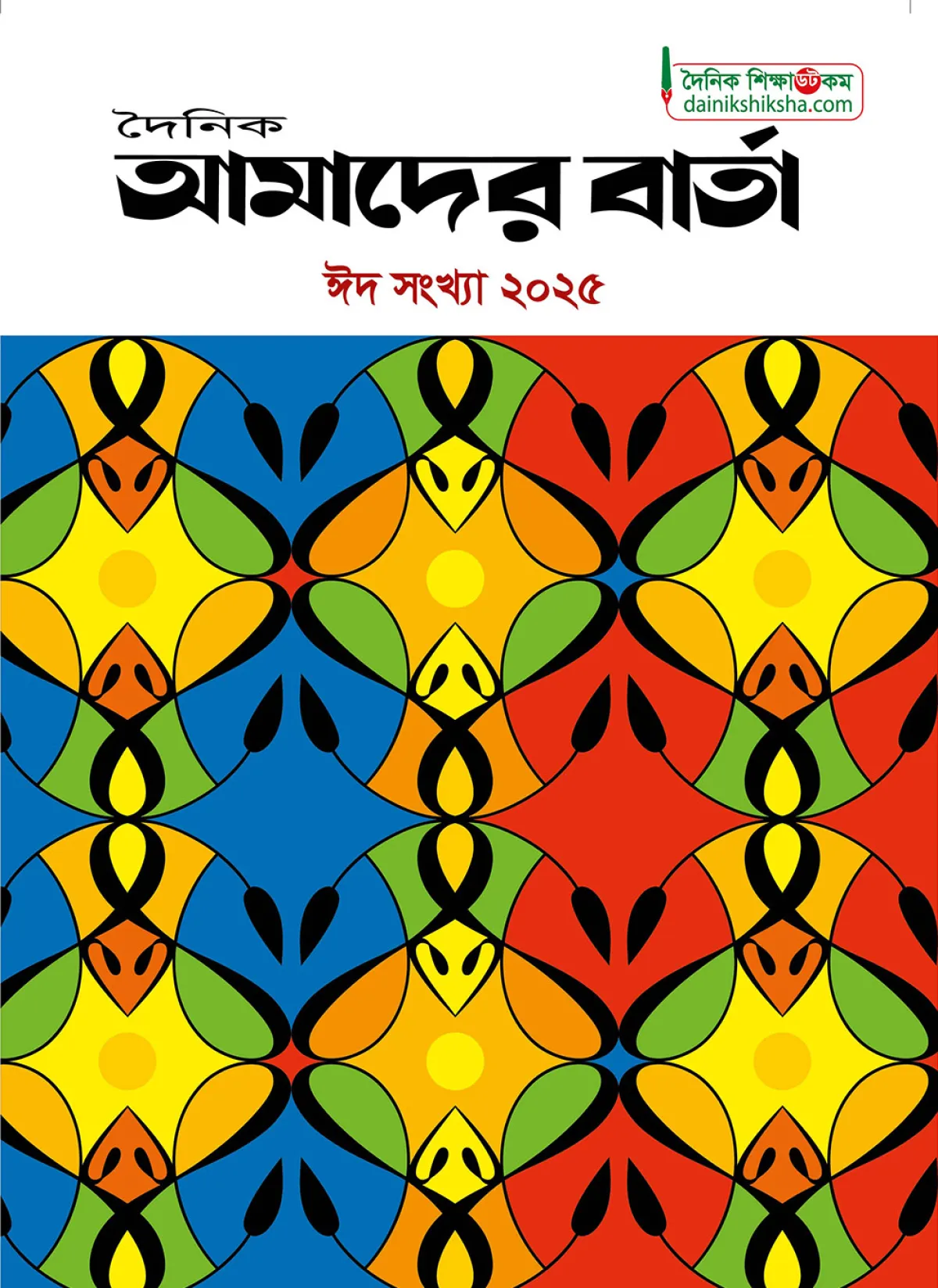
লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি, আমাদের ক্ষেত্রে যেটা করেছি- আমি যদি এখন প্রথমেই হাত দেই যে, ঠিক আছে একদম ঢালাওভাবে সব পরিবর্তন করতে চাই, যে পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স হবে, আমার এখনকার যে বাস্তবতা, বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র এবং জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেখানে আমাকে প্রতিদিন টিকে থাকার লড়াই করতে হচ্ছে, আমার পক্ষে খুব বেশি বড় পরিসরে হঠাৎ করে রিফর্ম করা কঠিন।
অতএব, আমি কিছু ভালো উদাহরণ তৈরি করতে চাই। সেই উদাহরণগুলো থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা এটাকে যখন গ্রহণ করবেন, ওই উদাহরণটা থেকে আমরা সাপোর্ট তৈরি করবো এবং তারপর থেকে স্কিল আপ করবো। একটা উদাহরণ দেই- আমার যে রিসার্র্চ সেন্টারগুলো আছে, এখন রিসার্চ সেন্টারগুলোতে আমরা সার্চ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দিচ্ছি। আর আগে এটা লিটারেলি ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দিতে পারতেন। তিনি যাকে খুশি তাকে দিতে পারতেন। এখানে রাজনৈতিক বিবেচনা মুখ্য হতো।
আরো পড়ুন:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বিশেষ সাক্ষাৎকার-প্রথম পর্ব
ঢাবি জনসংযোগ পরিচালকের সাক্ষাৎকার
এখন আমি যেটা করেছি, ভাইস চ্যান্সেলর ক্ষমতা কমিয়ে ফেলছি। এজন্য আমি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম করেছি। ভাইস চ্যান্সেলর সিদ্ধান্তগুলো এককভাবে নিতে পারবেন না। আমার প্ল্যান হচ্ছে, টাকার পরিমাণও লিমিট করে দেওয়া। যেমন- দশ লাখ টাকা, পাঁচ লাখ টাকা, আমি চিন্তা করছি কীভাবে করা যায়। একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশি টাকা সাইন করতে গেলেই দুটি সিগনেচার লাগবে। এককভাবে ভাইস চ্যান্সেলর করতে পারবেন না।

ঠিক একইভাবে আমরা যেটা করছি নিয়োগের ক্ষমতা কমিয়ে ফেলার জন্য, আমরা একটা সার্চ কমিটি করেছি। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, যাদের সরাসরি কোনো কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট নেই, তারা এই সার্চ কমিটির সদস্য হবেন। তারা তিনটি নাম দেবেন। সেই তিনটি নাম থেকে একজনকে নেবেন। এর বাইরে যেতে পারবেন না।
এভাবে আমরা আমাদের দুটি প্রধান সেন্টারে অলরেডি নিয়োগ দিয়েছি। একটি হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, আরেকটি হচ্ছে বিজ্ঞান উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র। দুটিতেই ভালো ফল পেয়েছি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই উদাহরণগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে আমরা এরপর লেকচারারের জন্য প্রয়োগ করবো, ডিনদের জন্য প্রয়োগ করবো। আস্তে আস্তে এটা করতে হবে। যাতে আমি কিছু ভালো উদাহরণ তৈরি করতে পারি।
আমরা একটা কমেটি করে দিয়েছি এটা দেখবার জন্য যে, আমরা পিএইচডি বাধ্যতামূলক করবো কোন পর্যায় পর্যন্ত। জেনারেল পর্যায়ে এটা কারো কারো জন্য বিলাসিতা হতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষকের জন্য এটা পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত। আমি এটাই মনে করি।
আপনার বক্তব্যের মধ্যে ফ্যাসিলিটির কথা এলো, পিএইচডির কথা এলো। কিন্তু, গবেষণার মান নিয়ে কী বলবেন? বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণা কার্যক্রমগুলো হচ্ছে, আপনি আসার পর যেগুলো পেয়েছেন, এগুলোকে বিশ্বমানের সাথে তুলনা করলে আমরা কোন পর্যায়ে আছি?
প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা র্যাঙ্কিং নিয়ে আলাদা একটা উদ্যোগ নিয়েছি। একদম শুধু র্যাঙ্কিং দেখার জন্য। সংশ্লিষ্ট মণ্ডলীদের সাথে কথা বলে আমি বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছি। যেমন- জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, ভালো জার্নাল যদি কেউ ছাপান, তার খরচটা আমাদের যত বাজেট সীমাবদ্ধতা থাকুক, আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টাকাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভালো জার্নাল ছাপালে, জর্নাল ছাপানোর খরচটা আমরা দিচ্ছি। রিসার্চ প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বাজেট কাট করছি না। এমনিতেই বাজেট কম, যতদূর আছে রিসার্চের ক্ষেত্রে কাজ করছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা গবেষণা প্রজেক্ট জমা দিচ্ছেন, তাদেরকে পূর্ণ ফ্যাসিলেশন দিচ্ছি। আমার দপ্তরে আমি দিনেরটা দিনে শেষ করার চেষ্টা করছি। কোনো সময় পারছি, আবার কোনো সময় পারছি না। কিন্তু দিনেরটা আর এক সপ্তাহ আটকে থাকবে না। সম্ভাবনা নেই।

কিছু উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা করে টিকে আছে, টিকে থাকতে পারে, এরকম শিক্ষক আমাদের আছে। মুশকিল হচ্ছে অতি রাজনীতিকরণের কারণে এরা বেশিরভাগই ডুব দিয়ে থাকছে। তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে আইডেন্টিফাই করে পূর্ণ ফ্যাসিলিটেট করা, সহযোগিতা করার কাজটা আমরা খুব সিস্টেমেটিক্যালি আগে করতে পারিনি। এখন সেটা করার চেষ্টা করছি। আমি তো কোনোরকম কোনো দলমত কিছু না দেখে, আমাদের যারা সবচাইতে ভালো পাবলিকেশন করেছেন এবং যাদের নাম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লিস্টে আছে, তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি। আইপিএসসির তরফ থেকে আমরা বলেছি যে, ট্রেনিং প্রশিক্ষণের জন্য বলেছি।
একটা ফাউন্ডেশন কোর্স আমরা সব শিক্ষকের জন্য চালু করতে চাই। সিভিল সার্ভিসেরও ফাউন্ডেশন কোর্স আছে। বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আসবেন, তারা পদ্ধতিগতভাবে পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপর ক্লাসে যাবেন। এটিকে আমি ধীরে ধীরে করতে চাই, তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এবার সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাসে আইপিএসসির নেতৃত্বে একটি ফাউন্ডেশন কোর্স এবার রান করলাম। আগেও আমাদের এটা দুয়েকবার হয়েছে, কিন্তু ফাউন্ডেশন কোর্স তখন ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। এবার আমরা পরিকল্পিতভাবে করছি, যাতে এটাকে বাধ্যতামূলক করতে পারি। যেন নতুন যারা শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন, তারা প্রত্যেকেই ফাউন্ডেশন কোর্স করে আসবেন। এবং তাতে অনেকগুলো বিষয় ইনক্লুডিং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, পাবলিক স্পিকিং, একজন শিক্ষক পরিষ্কার বাংলায় বা ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন- এই ব্যাপারগুলো আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।
আমরা এখনো আন্তর্জাতিক মানে অনেক পিছিয়ে আছি। কিন্তু আমাদের ভেতরে পটেনশিয়াল আছে। আমাদের এখনো ২০-২৫ ভাগ শিক্ষক আছেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু এই ব্যক্তি হিসেবে তার যে অর্জন, তার আমি প্রাতিষ্ঠানিকরণ করতে পারি না। সেটা যদি আমি করতে পারি, অটোমেটিক্যালি আমি কিছু বেনিফিট পাবো। সেজন্য আমি ঠিক ওই পথেই যাচ্ছি। তাতে আপনি কিছু পরিবর্তন হয়তো দেখবেন, তিন-চার মাসের মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিছু র্যাঙ্কিংয়ে আমরা চার-পাঁচ ধাপ এগিয়েছি। লং ওয়ে টু গো।

আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমার মনে হচ্ছে সমস্যাগুলো কোথায় মোটামুটি তা আইডেন্টিফাই করেছি এবং সইে অনুযায়ী একেকটা স্টেপ নিচ্ছি। সময় লাগবে। আই থিংক, উই আর ইন দ্যা রাইট ট্র্যাক।
একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে যে, বাই ডিফল্ট ডাকসুর সভাপতি হচ্ছেন ভিসি। সবাই বলছেন, ভিসি কেন সভাপতি থাকবেন? এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?
আমার ব্যক্তিগত অভিমত যদি বলেন, আমি ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা কমিয়ে ফেলার পক্ষে। যেখানে যেখানে সম্ভব। এটা হলো আমার অবস্থান। এই ব্যাপারটার জন্যই আমরা কমিটিগুলো করে দিয়েছি। অল গঠনতন্ত্র সংশোধনে একটা পরিষ্কার কমিটি আছে, ছাত্রদের সাথে সিস্টেমেটিক মিটিং করছে তারা। তারা যদি বৃহত্তর সংগঠনের ভিত্তিতে বলে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।
আপনার বক্তব্যেও ভেতরে কিন্তু শিক্ষাখাত এবং এনজিও খাত- দুটোরই ডেসক্রিপশন পাচ্ছি। আপনি একাধিকবার স্কেল আপ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটি আসলে এনজিওতে সুপরিচিত শব্দ। শিক্ষায় তেমন একটা ব্যবহার হয় না। এই দুই খাতের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যারেক্টারটাও আলাদা। যেমন আর ফর রেসপনসিবিলিটি। শিক্ষা রেসপনসিবিলিটি শেখায়। আবার আর ফর রাইটস। যার চর্চা এনজিওতে বেশী। এই দুটোর ভেতরে কীভাবে সমন্বয় হতে পারে?
প্রথম কথা হচ্ছে, আমি চাই সমাজের সব প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে চলতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনি সর্বজনীন একটা প্রতিষ্ঠান বলেন। এটা এনজিওরও প্রতিষ্ঠান, এটা সরকারেরও প্রতিষ্ঠান, এটা শ্রমিক বা রিকশাওয়ালারও প্রতিষ্ঠান। আবার এটা প্রফেসর ইউনূসেরও প্রতিষ্ঠান। এই মানসিকতা যদি আমাদের থাকে, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে আমার শক্তি হচ্ছে সমাজকে নিয়ে চলা।

আমি সরকারের ওপর যতো নির্ভর করবো, আমার মেরুদণ্ড ততো দুর্বল হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক সরকার এলে, তাদের যদি পূর্ণ সদিচ্ছাও থাকে.... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাথা উঁচু করে চলতে হলে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। পূর্ণ সদিচ্ছা থাকলেও আমাদের যে মাপের রিসোর্স দরকার, এটা সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা যতো বাড়বে, ততো আমার স্বায়ত্তশাসনের জন্য হুমকি বাড়বে। এবং সেটি বুঝতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে যে, তাহলে আমার শক্তি কী? এই মুহূর্তে আমার শক্তি কী? আমার পেছনে কোনো পুলিশও নেই, কোনো ছাত্র সংগঠনও নেই যে আমাকে সারাক্ষণ প্রটেকশন দিচ্ছে। আমি মূলত নির্ভর করছি আপনাদের ওপর।
আমার ওপর একটা আক্রমণ আসতে পারে, যদি আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলি এই কাজটা আমি চেষ্টা করছি সাপ্তাহিকভাবে করতে। আমি এতো দূর করতে পারলাম ভাই, এতদূর আমি পারছি না অমুকের কারণে। আমার ধারণা যে, মানুষ আমার পেছনে থাকবে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শক্তি। এবং ভাইস চ্যান্সেলরদেরকে এভাবেই চালাতে হবে। সেটা চালানোর জন্য আমাকে সার্বক্ষণিক সমাজকে নিয়ে চলতে হবে। যেখানে যেখানে সুযোগ আছে, অভিভাবকদের কাছে যাওয়া....। আমি এটা সব সময় বলি, আপনাদেরকে আবারো বলছি, আমার যদি আজকে ক্ষমতা থাকতো, আমার এই ৪২ হাজার শিক্ষার্থীর বাবা এবং মাকে আমি ডেকে আনতাম। ডেকে একটা বিরাট মাঠে দাঁড়াতাম এবং তাদেরকে শুধু বলতাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিশ্বাস করে আপনাদের সন্তানের দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনাদেরকে সালাম জানাই। শুধু এই কথাটুকুই বলবো, সমাজকে নিয়ে আমাকে চলতে হবে এবং এর কোনো বিকল্প নাই।

সমাজ যখন আমার পেছনে দাঁড়াবে, তখন এই ক্ষতিকারক শক্তিগুলো বিশেষ করে ক্ষতিকারক রাজনৈতিক শক্তিগুলো দুবার ভাববে আমাকে ঘাঁটানোর আগে। এটা পরিষ্কার কথা। রাজনৈতিক শক্তির মধ্যেও অনেক শুভশক্তি আছে। দুর্বৃত্তায়নের কারণে তুলনামূলকভাবে এই শুভ শক্তিরা এখন চাপা পড়ে যাচ্ছে। তারাও তখন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। আমার ভিত্তি তৈরি করার প্রধান উপায় হচ্ছে এটা যে, সমাজকে নিয়ে চলতে হবে আমাকে। যেখানে যেখানে সম্ভব, এনজিওকে নিয়ে চলবো। আমি ভলান্টিয়ার এজেন্সিগুলোকে নিয়ে চলবো। অভিভাবকদের নিয়ে চলবো। যেখানে যা সম্ভব, আমি সেটা করতে চাই।
গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটা স্বপ্ন সবার মাঝে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে কন্ট্রিবিউশন করতে পারে বা নেতৃত্ব দিতে পারে?
আরো অনেকবারের মতোই এবারো এই আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো কিন্তু আমি এককভাবে কোনো কৃতিত্ব নিতে চাই না। আমরা মনে করি, আমাদের মূল ভূমিকা হবে সবাইকে সাথে নিয়ে চলা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা বিশাল ভূমিকা ছিল। আমি সব সময় চাই তারা আমাদের সাথে থাকুক। আমি চাই রিজিওনাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের সাথে থাকুক। পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় আমার সাথে থাকুক। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমার সাথে থাকুক। আমি চাই যে, আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা নিবিড় হোক। আমি চাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং আমাদের শিক্ষকরা মিলে আমরা যৌথভাবে প্রজেক্ট সাবমিট করি। রিসার্চগুলো যৌথভাবে করি। এই বিভেদ আমাদের কমাতেই হবে। এবং এটাই আমাদের শক্তি।
সম্প্রতি একটি বিষয় খুবই আলোচিত হচ্ছে যে, শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করবেন শিক্ষকদের, এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?
জি¦। আমরা পদ্ধতিগতভাবে একটা কাঠামো তৈরি করছি। অলরেডি আমাদের একটি ফর্ম আছে টিচিং ইভ্যালুয়েশনের ওপর। সেই ফর্মটি এখন কিছু কিছু বিভাগ অপশনাল হিসেবে প্রয়োগ করছে। অনেক বিভাগই করছে। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ যেমন করে। আবার এটি যেহেতু বাধ্যতামূলক নয়, তাই কেউ কেউ করছে না। আমরা চাচ্ছি এটার ব্যাপারে একটা বৃহত্তর সমঝোতা করে এটা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া। যাতে একটা পদ্ধতিগতভাবে ছাত্ররা তাদের শিক্ষকের মূল্যায়ন করতে পারেন। যে সার্ভিসটা তিনি পেয়েছেন, তাতে কতটুকু তিনি হ্যাপি আছেন, কতটুকু নেই।
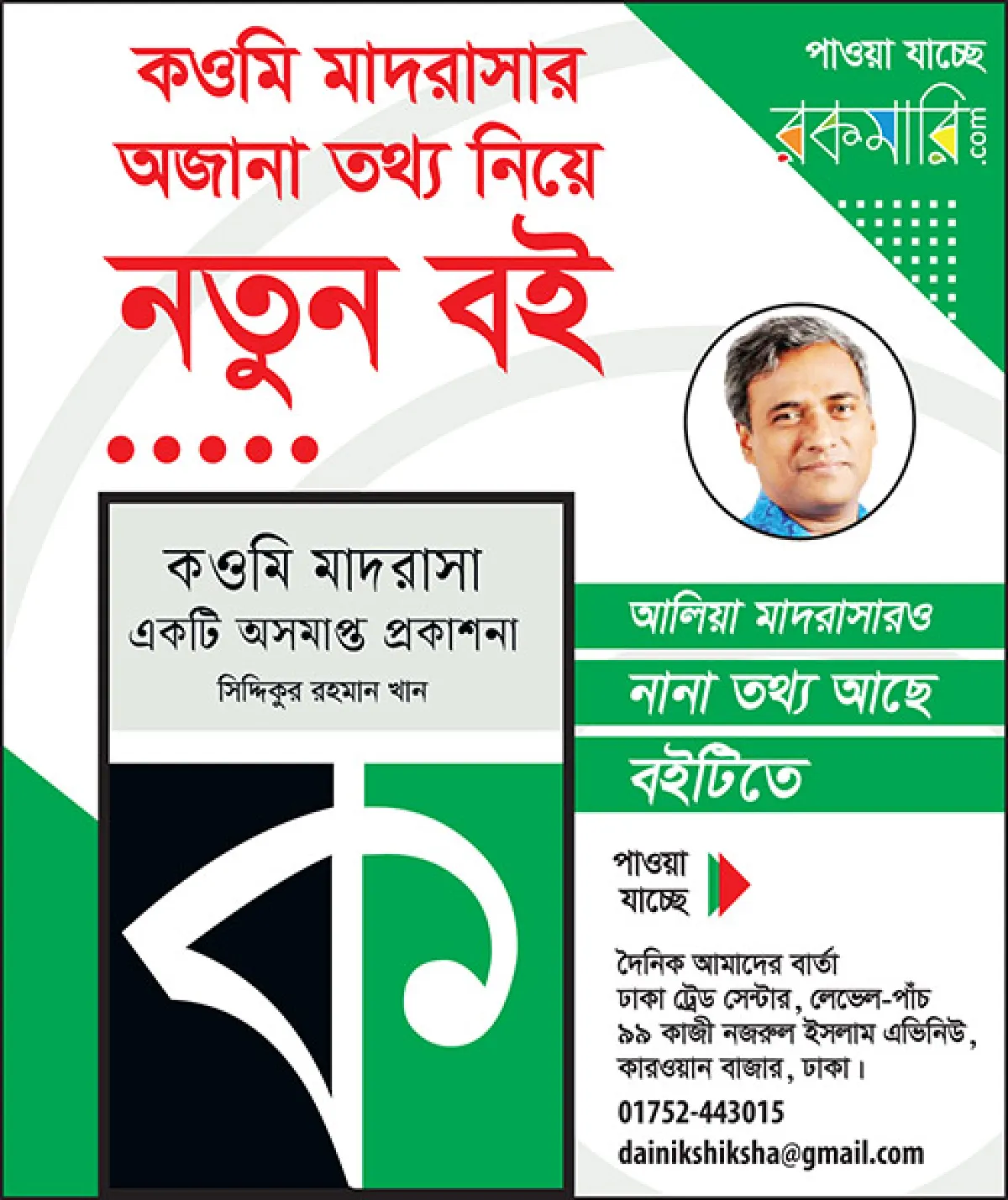
শিক্ষকদের তো টিকে থাকতে হবে। আমাদের ওপর ছাত্রদের ট্রাস্ট এবং আমরা আমাদের সার্ভিসটা তাদেরকে কতটুকু দিতে পারলাম? সেটি যতো গ্রহণযোগ্য হবে, ততোই আমার শক্তি বাড়বে। আমার সম্পর্কে আমার ছাত্ররা কী বলে? সেটিই আমার প্রধান মাপকাঠি। আর এই পদ বা যাই বলুন না কেন, এটি কিন্তু একদমই সাময়িক। আর আমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে বলেন, আমি এটাকে একটা দায়িত্ব মনে করছি। একটা নির্দিষ্ট বাস্তবতায় এই দায়িত্বটা আমরা নিয়েছিলাম। এবং আমি এটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে চলে যেতে চাই। আমি একজন শিক্ষক, আমি শিক্ষকতায় ফিরে যেতে চাই।
সারা দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন ....
সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্কগুলোর একটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। বিভিন্ন কারণে আমাদের কিছু কালো দাগ লেগেছে। কিন্তু এগুলো অতিক্রম্য। আমরা সবাই মিলে কাজ করলে, এই সম্পর্কটা এতোই পবিত্র যে আমরা যদি নিজেদেরকে বিসর্জন দিতে পারি, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী সম্পর্কে পরিণত হবে। আমরা সব কাজ করেছি, করে দেখিয়েছি। অতএব এই শক্তি, ছাত্র-শিক্ষক শক্তি থাকলে, বৃহত্তর পর্যায়ে জাতি উপকৃত হবে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এর শক্তি ব্যবহার করতে পারবো।
গ্রন্থনা: এম মাহবুব আলম ও সাদ আদনান, আলোকচিত্র: বুলবুল আহমেদ