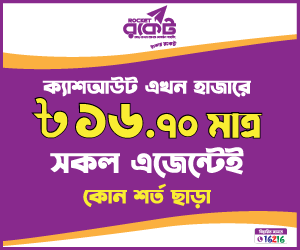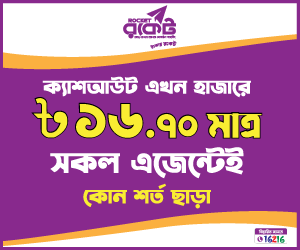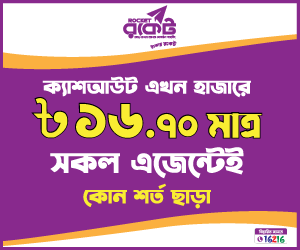একবার ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। সে যাত্রায় দলনেতা ছিলেন ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া। ফ্রান্সে আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো না, প্রোগ্রাম ছিলো জেনেভায়। সেনজেন ভিসার একটা সুবিধা হলো, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত সব দেশে একই ভিসায় যাওয়া যায়। সে সুযোগটাই কাজে লাগলো। বিশ্বসভ্যতার কতো কিছুই না দেখার আছে ফ্রান্সে। ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতিমুখর বাস্তিল দুর্গ, সপ্তাশ্চর্যের একটি আইফেল টাওয়ার, ল্যুভর মিউজিয়ামসহ কতো কিছু। তাই ডেপুটি স্পিকার যখন তার শুভানুধ্যায়ীদের আমন্ত্রণে ফ্রান্স যাচ্ছিলেন, তখন আমন্ত্রণ পেয়ে তার সফরসঙ্গী হতে আপত্তি করিনি। ওখানে যাবার পর সে দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম এক রাতে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন আমাদের। সেখান থেকেই শুরু আমার আজকের লেখা।
খাবার টেবিলে আমার পাশে বসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক, আমাদের রাষ্ট্রদূতের বন্ধু এবং ওই সময়ে ঢাকার বিখ্যাত অ্যাপোলো (বর্তমানে এভার কেয়ার) হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। খাবার ফাঁকে তার কাছে জানতে চাইলাম ফ্রান্সে কবে এসেছেন, কবে ফিরবেন? তিনি জানিয়েছিলেন, তিন দিনের যাত্রা শেষে ফিরবেন পরশুই। এতো দ্রুত দেশে ফেরার কারণ জেনে বিস্মিত হলাম। তিনি বললেন, ঢাকায় তার ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। এই বয়সী একজন ভদ্রলোকের বাচ্চারা কান্নাকাটি করে, বিষয়টা হজম হলো না। মনের অজান্তে হেসে ফেললাম। আমার হাসি ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ালো না। উনি ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলেন। ঢাকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতে ইদানিং নতুন এক সিস্টেম চালু হয়েছে। বেশ কিছু প্রবীণ এখন সারা বছর হাসপাতালে থাকেন। না, অসুস্থ হয়ে নয়, জীবনের শেষ সময়ে যখন তাদের আত্মীয় পরিবেষ্টিত আনন্দসময় কাটানোর কথা। সে সময় তারা হাসপাতালে বাস করছেন চরম অবহেলা আর অনাদরে। এদের আর্থিক সংগতি আছে, কেউ কেউ সমাজে পদস্থও বটে, অবসরে চলে যাওয়া এসব বয়োবৃদ্ধের প্রায় সবার ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয় হলো কারো সন্তান-সন্ততিই কাছে থাকেন না। দেশে থাকা ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের ব্যস্ততা আর পারিবারিক সংকট এড়াতে, আর বিদেশে থাকা ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে নিজেদের কাছে না রেখে সমাজ তথা লৌকিকতার ভয়ে হাসপাতালের খরচ বাবদ কিছু টাকা দিয়ে দায় সারছেন। আজীবন সংসার চালানো ও সন্তানের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করে শেষ বয়সে গলগ্রহ হয়ে যাওয়া অসহায় এসব বাবা-মায়ের এক্ষেত্রে বলবারই বা কী থাকে? নিগৃহীত হবার চাইতে তারা মন্দের ভালো হিসেবে হাসপাতালের জীবন মেনে নেন। এখানে তো অন্তত খাবার চিন্তা নেই, শরীর খারাপ হলে প্রিয়জনের না হোক নেহায়েত চাকরির দায়ে আসা ডাক্তার-নার্সের সহযোগিতা হলেও পাওয়া যায়। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে মন চাইলে আসতে পারেন নিকটাত্মীয়দের কেউ কেউ। দীর্ঘদিন চিকিৎসায় কোনো কোনো নার্স ডাক্তারের সঙ্গে মানবিকতার একটা সম্পর্কও গড়ে ওঠে। ঠিক যেমন এই ডাক্তারের ক্ষেত্রে ঘটেছে। বৃদ্ধ ও অসহায় অশীতিপর রোগী পরিণত হয়েছেন তার সন্তানে। ডাক্তারের ব্যাখ্যা শুনে সে রাতে ঘুমাতে পারিনি। কেবলই মনে হয়েছে আমাদের জন্যও এমন জীবন অপেক্ষা করছে না তো? সেই থেকে মনের গহীনে কোথায় যেনো একটা প্রশ্ন কেবলই আমাকে ভাবায়; কখনো কখনো কাঁদায়ও।
আমার ভাবনাটা যে অমূলক নয় তার উদাহরণ তো ভুরি ভুরি। বাংলা চলচ্চিত্রে ‘নবাব সিরাজউদ দৌলা’-খ্যাত আনোয়ার হোসেনের একসময় টাকা, যশ, খ্যাতি--কোনোটারই অভাব ছিলো না। জীবনে উপার্জিত সব অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন সন্তানদের পেছনে। তাদের বিদেশ পাঠিয়েছেন। তিন সন্তানের মধ্যে দুজন আমেরিকায়, আর এক জন থাকেন সুইডেন। কিন্তু সন্তানরা প্রতিষ্ঠা পেলেও বাবার খবর নেননি। আনোয়ার হোসেনকে তাই বৃদ্ধকালে অসুস্থ শরীরে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে জীবন বাঁচাতে হয়েছিলো। তার মৃত্যুর খবর পেয়েও সন্তানরা আসেননি। চরম অবহেলায় আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় অনেকটা বেওয়ারিশ লাশের মতো দাফন করা হয়েছে হতভাগ্য এই মহান শিল্পীকে। বিখ্যাত কবি আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। তিনি তার শেষ সম্বল বনানীর বাড়ি বিক্রি করে সন্তানকে বিদেশ পাঠিয়ে রাজধানী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনিও জীবনের শেষ সময়টা নিতান্ত একাকিত্ব ও অবহেলায় কাটিয়ে ফিরে গেছেন না ফেরার দেশে। কয়েক বছর আগে আমাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে তার নিজ ফ্ল্যাট থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন তার পুত্র। চলৎশক্তিহীন অশীতিপর এই বৃদ্ধকে রক্ষা করতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে।
তাহলে আমরা যে পরবর্তীতে এমন ঘটনার শিকার হবো না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? কাজেই ভাবতে হবে এখন থেকেই। ওই যে কথা আছে না ‘সময় গেলে সাধন হবে না’। পশ্চিমবঙ্গের কণ্ঠশিল্পী নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে একটা গান আছে। গানটি হলো, ‘ছেলে আমার মস্ত বড়, মস্ত অফিসার…’
গানটার প্রতিটি বর্ণই যেনো এক করুণ পরাবাস্তবতা। জেনারেশন গ্যাপ বা প্রজন্ম-বৈসাদৃশ্যের কারণে আমাদের জেনারেশনের অবস্থা এখন সবচেয়ে সংকটাপন্ন। ওই অনেকটা আকাশ থেকে পাতালে পড়ার মতো। পরিবর্তনগুলো সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করেছি আমরাই। আমরা বিদ্যুৎবিহীন হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় পড়াশোনা করেছি, বিদ্যুৎবিহীন রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শিখেছি ধ্রুবতারা, শুকতারা, কালপুরুষ, লুব্ধক প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রের নাম। আর এখন দেখি এলএডি বাতির সব ফকফকা আলো।
’৯৬ তে বিসিএস করে সরকারি চাকরিতে ঢুকলাম। গোপালগঞ্জে কর্মক্ষেত্র। মায়ের লেখা চিঠি পেয়েছি পাঠানোর ১২/১৩ দিন পরে। কতো প্রতীক্ষা, কতো আকুলতা আর কতো ভালোবাসা ছিলো সে চিঠিতে। আর এখন তো চিঠির প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে। ইথার যোগাযোগ এখন ফোরজি থেকে ফাইভজি’ তে ছুটছে। কিন্তু এই উল্লম্ফনের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো কেনো? আমরা তো এ প্রজন্মের বিবেচনায় মূর্খ, সেকেলে। তাই প্রজন্মের এই ব্যবধানটা আমাদের বড় পোড়ায়, বড় আহত করে।
এমনিতেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে একটা গ্যাপ থাকে। যেমন-আমাদের সঙ্গে আমাদের বাবা-মায়েদের ছিলো। হয়তো তাদেরও ছিলো তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের ব্যবধানটা বড্ড বেশি। আমাদের প্রজন্মে আমরা এই বোধটা নিয়ে বড় হয়েছি যে, বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে দেখভালের দায়িত্বটা আমাদেরই। আমাদের আগের প্রজন্মের ধারণা ছিলো কন্যা সন্তান বিয়ে থা করে অন্যত্র চলে যাবে। ছেলে সন্তানকেই উত্তরাধিকার সংরক্ষণ থেকে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ভরণপোষণের দ্বায়িত্ব নিতে হবে। তাই পরিবারে ছেলেসন্তান অনেক বেশি আদরের ছিলো। কিন্তু এখনকার বাস্তবতা ভিন্ন। নারী শিক্ষার বিকাশের কারণে মেয়েরাই এখন বাবা-মায়ের দেখাশোনা করেন বেশি। ওটাই বোধ হয় জেনারেশন গ্যাপ। আজকালের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ব্যস্ত ওদের ক্যারিয়ার নিয়ে। নিজেদের সাফল্যের ঠিকানা খুঁজতে ওরা আকাশ-পাতাল এক করছে, কেউ কেউ ছুটছে দেশ থেকে দেশান্তরে। ওদের এতো সময় কোথায় এসব বুড়ো অথর্ব মানুষকে নিয়ে ভাবার? এতে ওদের দায় যতোটা, তার চেয়ে আমাদের দায়ই বেশি। আমরাই তো ওদের মাথায় গেঁথে দিয়েছি ‘Survival of the fittest’ এর থিওরি। শেখাইনি Social responsibility-র সূত্র। ওদের বলিনি, শুধু সামনে এগুনোই নয়, পেছনেও তাকাতে হবে। অসহায় আর্তদের হাত ধরে তুলে আনতে হবে ভালোবাসাময় মানবিক পৃথিবীতে। ওটাই আমাদের মূল্যবোধ, ওটাই আমাদের সমাজেরও ।
আগে একটা লেখায় বলেছিলাম আকাশ সংস্কৃতির কালো থাবায় বিশীর্ণ আমাদের সমাজ। যন্ত্রের সঙ্গে খেলতে গিয়ে আমাদের শিশুরা মানবিক হবার পরিবর্তে হয়ে পড়ছে যান্ত্রিক। মায়া-মমতা- ভালোবাসা প্রায় নির্বাসিত আজ ওদের অন্তর থেকে। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে পরকীয়া বাড়ছে, নারীদের ক্ষমতায়নের নামে নারী নির্যাতনের পাশাপাশি বাড়ছে পুরুষ নির্যাতনও। বড়দের মধ্যে সহনক্ষমতা কমছে। তুচ্ছ ঘটনায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে অনেক পরিবারে। অথচ আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, বিয়ে বিচ্ছেদ ছিলো যেকোনো পরিবারের জন্য কঠিন এক সিদ্ধান্ত। একটি পরিবারে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরিবারের অন্য মেয়েদের বিয়ে দেয়া দুরূহ হয়ে যেতো। ফলে কথায় কথায় ছাড়াছাড়ির এ প্রবণতা ছিলো না। আজকাল এসব ছাড়াছাড়ি বিষয়ে হাজারটা যুক্তি হয়তো দেয়া যাবে, কিন্তু দিনশেষে এসব বিচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানরা। ফলে সন্তানদের মধ্যে বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। বাড়ছে জিঘাংসা। আমাদের জেদ, অহং এসবেরই হয়তো জয় হচ্ছে। কিন্তু সমাজে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ঐশী, যাদের কাছে সর্বত্যাগী বাবা-মা আলাদা কোনো শ্রদ্ধা পায় না। ফলে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ে। বাড়ে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের হতাশা, কষ্ট।
‘৮০র দশকে ঢাকায় তেমন কোনো বৃদ্ধাশ্রমের অস্তিত্ব ছিলো না। আগারগাঁওয়ে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ নামে অবসরে যাওয়া বৃদ্ধদের একটি ক্লাব ছিলো। সেটাই এখন ডালপালা ছড়িয়ে ৮/১০ তলা ভবন হয়েছে। কলেবর বেড়েছে। বেড়েছে এর বাসিন্দাও। একেকজন বাসিন্দার জীবন যেনো একেকটি স্বপ্নভাঙা হতাশার মহাকাব্য। আমরা কজন তার খোঁজ রাখি?
গেলো ২০/৩০ বছরে গাজীপুর, সাভার, ঢাকায় কয়েকটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। এসব বৃদ্ধাশ্রমে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের আশ্রয় হলেও উপেক্ষিত হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অথচ এ সমাজে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছেন এরাই। মধ্যবিত্তরা নিম্নবিত্তের মতো সাহায্য নিতে পারেন না। সংস্কারে বাধে। আবার উচ্চবিত্তের মতো আকাশ ছোঁয়ার সামর্থ্যও নেই তাদের।
একবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রবীণ নিবাসে গিয়েছিলাম। ঈদের আগে আমাদের কয়েকজন বন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে উপহারসামগ্রী দিতে। দেখা হলো আমার এক শিক্ষকের সঙ্গে। বয়স, জীবন সংগ্রাম ও হতাশায় তিনি। চেনাই যাচ্ছিলো না তাকে। কাছে গিয়ে ডাকলাম, ‘স্যার’। পুরু কাচের চশমায় স্যার একবার তাকালেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের কাজে। আমাকে চিনলেন না, কিংবা চিনতে চাইলেন না। আমি কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম। কী বলবো, বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘শরীর কেমন?’ নির্লিপ্ত স্বগতোক্তিতে জানালেন, ‘ভালো।’
‘স্যার কিছু লাগবে?’ জানতে চাইলাম। স্যার জবাব দিলেন ‘না’। আমি একটা পাঞ্জাবি তার টেবিলে রাখলাম। বললাম, ‘স্যার, আমার বাসা কাছেই, ঈদের দিন আসবো। আপনাকে নিয়ে যাবো, আমাদের সঙ্গে ঈদ করবেন।’ হঠাৎ কেনো যেনো উনি ক্ষেপে গেলেন। টেবিলে রাখা পাঞ্জাবিটা ছুঁড়ে ফেললেন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। এক পর্যায়ে মন খারাপ করে যখন প্রস্থানোদ্যত হয়েছি, তখন মনে হলো কে যেনো আমার পিঠ স্পর্শ করে আছেন। ঘুরতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার স্যার। আমার প্রিয় স্যার, যার দেয়া জ্ঞানে আমার এ পথচলা। বললেন, ‘রাগ করেছিস? কেউ করুণা করলে নিতে পারি না। পরিচিতদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকি। তুই সাহায্য করতে চাইলি, আমার ভালো লাগেনি, তাই রেগে গিয়েছিলাম’।
আমি স্যারকে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। উনি আমার বর্তমান অবস্থান জেনে খুশি হলেন। বললেন নিজের কথাও। স্যারের দুই মেয়ে, এক ছেলে। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেক আগেই। অতি আদর আর বাবা-মায়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনে বখে গেছে ছেলেটা। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে। বড়টা থাকে বিদেশে। ছেলে ব্যবসা করবে বলে বাবার পেনশনের টাকাগুলো নয়ছয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, চাপ দিচ্ছে গ্রামের অবশিষ্ট ভিটেমাটি বিক্রি করে টাকা দিতে। স্যার আপত্তি করেছেন। তাতেই ঘটেছে বিপত্তি। বচসা থেকে হাতাহাতি। সন্তানের হাতে নিগৃহীত হয়ে শেষমেশ এক ছাত্রের সহযোগিতায় ঠিকানা হয়েছে এখানে। নতুন ঠিকানায় আসার পর একদিনের জন্যও ছেলে খবর নেয়নি বাবার। ছোট মেয়েটা স্বামীর চোখ বাঁচিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু খাবার, কিছু টাকা পাঠায়। স্যার ওসব নিতে চান না। তার আত্মসম্মানে লাগে। বছর দুয়েক আগে বড় মেয়েটা মাস দুয়েকের জন্য দেশে এসেছিলেন। একদিন মিনিট পনের ছিলেন বাবার সঙ্গে। তবে বড় মেয়ের ঘরের নাতিটা খোঁজ রাখে। বিদেশ যাবার আগে নানাকে জোর করে একটা মোবাইল দিয়ে গিয়েছিলো। ওটা দিয়েই যোগাযোগ হয় দুজনের। নিজের বৃত্তান্ত জানাতে গিয়ে বারবার স্যারের গলা ভারী হয়ে আসছিলো। পুরু কাচের চশমার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, স্যার কাঁদছেন। আমি আর নিতে পারছিলাম না। নিজের মধ্যে নিজে বারবার ভেঙে পড়ছিলাম। দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে স্যারকে ‘আবার আসবো’ বলে চলে এলাম।
আমার বাবা গত হয়েছেন ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে। মা ২০১৯-এ। এখনো তাদের কথা মনে হলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অথচ স্যারের ছেলেমেয়েরা জীবিত বাবার খবর রাখেন না। ভাবতেই স্যারের মতো আমারও একরাশ ক্ষোভ জমা হয়েছিলো ওই পাষণ্ড ছেলেমেয়ের ওপর। আমার বাসার খুব কাছে আগারগাঁও। পরিচিত দু-একজন কাজ করেন ওখানে। ওদের একজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমার কথা গোপন রেখে স্যারকে যেনো সাহায্য করে। কিছু টাকা দেয়া ছিলো তাকে। ২০১৯-এর শেষভাগে তখন কোভিডের বিস্তার সবে শুরু হয়েছে। একদিন ওই ভদ্রলোক আমার অফিসে এলেন। ভাবলাম হয়তো স্যারের জন্য কিছু দরকার। কিন্তু উল্টো আমাকে কিছু টাকা ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন স্যারের চলে যাবার খবরটা। বিদেশে থাকায় স্যারের শেষ যাত্রায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। কিন্তু তার এ চলে যাওয়ায় মনে হলো আমার দ্বিতীয়বার পিতৃবিয়োগ হলো। শেষ সময়ে তার জন্য কিছু করতে না পারার কষ্টটা হয়তো জ্বালাবে আজীবন। এ ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। পীড়িত বোধ করছি মধ্যবিত্ত অর্থাৎ আমাদের শ্রেণির এসব অসহায় বৃদ্ধ মানুষের জন্য কিছু একটা করার। সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের বৃদ্ধাশ্রম হতে পারে সেরা উপায়। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তবতা তো এক নয়। আমি প্রায় নয় বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। প্রথমে ভেবেছিলাম একাই কিছু একটা করবো। কিন্তু মাঠে নেমে দেখলাম বিষয়টি এতো সহজ নয়। এর জন্য দরকার জায়গা, ভবন, স্থাপনা, পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান এবং একঝাঁক নিবেদিত কর্মী। ইচ্ছে ছিলো ঢাকার কাছাকাছি একটা বড় জায়গা নিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করবো কিন্তু জমির মুল্য ধারণাতীত বেশি। আমার মতো ছাপোষা সরকারি চাকরিজীবীর পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব। যদিওবা ছোটোখাটো একটা জায়গা কিনে শুরু করি, কিন্তু ভবন নির্মাণ, মাসিক পরিচালনব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণসহ প্রাসঙ্গিক খরচ চালানো একজন তো দূরের কথা, বহুজনের পক্ষেও কঠিন। আর একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করে বন্ধ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সমাজকল্যাণ বিভাগের উচ্চ পদে থাকা এক বন্ধু জানালেন, নিজেদের উদ্যোগে একটা স্থাপনা করে কার্যক্রম শুরু করলে সরকারি সহযোগিতার জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে আমাদের এ উদ্যোগ। তার জন্যও লাগবে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। দু-একজন সামর্থ্যবান মানুষের সঙ্গে কথা বললাম। কিন্তু তাদের প্রশ্ন হলো, এতে তাদের ব্যক্তিগত লাভ কী? একজন রাজনীতিবিদ বললেন, তার নামে তার এলাকায় হলে ভেবে দেখতে পারেন। কারণ, তাকে তো নির্বাচনের বিষয়টি দেখতে হবে। তিনবার হজ করে আসা এক ভদ্রলোক বললেন, ‘মাদরাসা করলে, আমি আছি।’ মনে হলো বৃদ্ধাশ্রম করা যেনো অধর্মের কাজ। আমার বিদেশে থিতু হওয়া এক বন্ধু দেশের জন্য কিছু করতে চান। তাকে আমার ইচ্ছের কথা বললাম। দেশে এসে ভাইসহ আমার সঙ্গে দেখা করলেন বন্ধু যতোই আগ্রহী হয়, তার ভাই ততোই নিরুৎসাহিত করে। ভাবটা এমন দেশের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তবে আমাদের জন্য করো। বৃদ্ধদের জন্য করে কী হবে? একজন ধনী বললেন, তিনি এতিমখানায় প্রতি বছর কিছু যাকাত দেন। তাই আমাদের বৃদ্ধাশ্রমেও কিছু টাকা দেবেন। তাকে বোঝালাম মধ্যবিত্ত মানে বোঝেন? এদের কিছু নেই, আছে শুধু আত্মসম্মান। এরা ভাঙে, কিন্তু মচকায় না। এরা না খেয়ে থাকবেন কিন্তু ভিক্ষা নেবেন না।
এতো সব নেতিবাচকতায় মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ি। ভাবি তবে কি ব্যর্থ হবে আমাদের এ মানবিক মিশন? কন্যাদেরও বলেছি, তোমাদের পড়াশোনার দায় শেষে ওটাই হবে আমাদের বৃদ্ধ বয়সের ঠিকানা। ওরা মেনে নিয়েছে। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে? তবে ইতোমধ্যে কিছু কিছু সাড়াও পাচ্ছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু হীরা কামরুল, রঙ্গন এগিয়ে এসেছে। দেশের শীর্ষ এক কর্মকর্তার একান্ত সচিব আগ্রহ দেখিয়েছেন। এরই মধ্যে প্রায় একইরকম একটা বড় প্রকল্প সফল করে আমাদের আরেক বন্ধু মাসুদ দেখিয়ে দিয়েছে, চেষ্টা থাকলে অনেক কিছু সম্ভব। সে নিজেও পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করছে। অনেকের কাছে শুনি প্রবাসীদের মধ্যে অনেকেই নাকি দেশে ফিরবেন না বলে তাদের ফেলে যাওয়া জায়গা-জমি ভালো কাজে লাগাতে চান। প্রাচীনপন্থি অনেকেই এতিমখানা করতে চান। কিন্তু তাদের কে বোঝায়, এখন এতিমখানার আবেদন শেষ হয়েছে। বৃদ্ধাশ্রমই এখন বেশি প্রয়োজন। কারণ, কে জানে এক সময় আমাকে-আপনাকেও হয়তো খুঁজতে হতে পারে এমন কোনো ঠিকানা। যাদের সন্তান আছে বা যাদের নেই সবারই প্রয়োজন হতে পারে এমন ঠিকানা। বাণিজ্যিক উদ্দেশে অনেকে আজকাল এ ধরনের বৃদ্ধাশ্রম তৈরির কাজ করছে। কিন্তু আমরা তেমনটা চাই না। পাঁচতারকা হোটেল নয়, আমরা চাই এমন এক ঠিকানা যেখানে চূড়ান্ত বিদায়ের আগের সময়টা কাটবে ছাত্রজীবনের মতো অপার আনন্দে। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অনুকম্পা বা গলগ্রহ নয়, অশীতিকে আমরা জয় করবো নিজেদের মতো করে। শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসায়। যার যেটুকু সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে আসুন সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি।
লেখক: উপ-সচিব