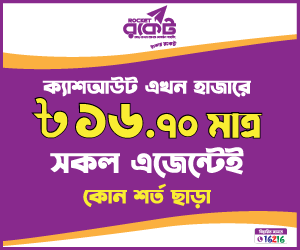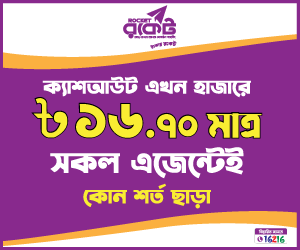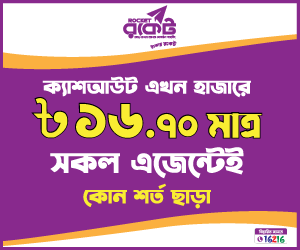১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের দিন। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের নাম জানান দেবার দিন। দেশ শত্রু মুক্ত হবার দিন। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক গৌরবময় দিন। বীরের জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ঐতিহাসিক দিন। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার দিন। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুসংহত, সুদৃঢ় করবার দিন। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শপথে বলিয়ান হবার দিন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার দিন।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একদিনে হয়নি, যুদ্ধের প্রেক্ষাপটও একদিনে তৈরি হয়নি। হাজার বছরের উপনিবেশিক শাসন, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের গড়ে তোলা এক আপোষহীন সংগ্রাম ও ত্যাগের ফসল এই মুক্তিযুদ্ধ। স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকার, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা পাকিস্তান আমলে সুদীর্ঘ ২৪ বছরের এই যাত্রা। একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাত্রির ভয়াবহতার পর আমাদের জনগণ পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তার শেষ পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ। যা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতি ছিলো ভীষণ স্বতন্ত্র। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আবেগ ও আবেগের প্রয়োগ ছিলো আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন নিজেদের যুদ্ধ নিজেরা করতে। যুদ্ধ করে নিজেদের বিজয় ছিনিয়ে আনতে। ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন নিজেদের দৃঢ় সংকল্প থেকে। দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন আবাসভূমি গড়তে। এই জন্যেই বিজয় দিবসের তাৎপর্য এতো হৃদয়স্পর্শী। রক্তসিক্ত ১৬ ডিসেম্বর এতো গৌরবদীপ্ত। দিনটি একদিকে জাতীয় স্বার্থে রক্তদানের আকুতির প্রতীক, অন্যদিকে আত্মশক্তির মহান প্রতিশ্রুতি। গৌরবময় বিজয়ের স্পর্শধন্য এক স্মরণীয় দিবস।
ঐতিহাসিকভাবেই ডিসেম্বর মাসকে আমরা বিজয়ের মাস রূপে গণ্য করি।
একাত্তরের মার্চে যার সূচনা, নয় মাস পর ডিসেম্বরেই তার চূড়ান্ত পরিণতি। তাই ডিসেম্বর এলেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগি। ডিসেম্বরে পা দিলেই অনুভব করি পায়ের নিচে শক্ত মাটির স্পর্শ। লাভ করি অনির্বচনীয় আত্মবিশ্বাস। ফিরে পাই অনিন্দ্য সুন্দর এক সুখানুভূতির উচ্ছ্বাস। ওইদিন বাংলার আকাশে বিজয়ের লাল সূর্য উদিত হয়। মানুষের মনে মুক্তির আনন্দ হিল্লোল জেগে ওঠে।
মুক্তিযুদ্ধের অর্জন আমাদের শ্রেষ্ঠতম অর্জন। যা সম্ভব হয়েছে জনগণের সাহস, শোর্য ও সীমাহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে। এই অর্জনের জন্য জনগণ বহু আগে থেকেই সচেতনভাবে উদ্যোগী হন। এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছেন পূর্ব বাংলার জনগণ। অর্থাৎ জাতীয় জনসমাজ বলতে যাদের বোঝায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তারাই অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ছেড়ে, কৃষকদের অনেকেই চাষাবাদ ছেড়ে, শ্রমিক মিল ফ্যাক্টরি ছেড়ে, পেশাজীবীদের অধিকাংশ নিজ পেশা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অনেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের নৈতিক ও ব্যবহারিক সমর্থন দিয়ে জাতীয় কর্মকাণ্ডের গর্বিত অংশীদার হন। শিল্পী সাহিত্যিকদের শিল্পকর্ম ও রচনা সম্ভার এই লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। দীর্ঘদিন পর জাতীয় পর্যায়ে জনগণের যে সার্বিক উদ্যোগ ও আত্মত্যাগের মহোৎসব তাই মুর্ত হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধে। বিজয় দিবস তারই গর্বিত ফসল।
মুক্তিযুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণ ছিলে অকুতোভয় সৈনিকের মতো। অনেকটা নিজেদের প্রণোদনায় নিজেরাই সেই পথ করেছিলেন রচিত। জাতি হিসেবে সগর্বে মাথা উঁচু করার অদম্য স্পর্ধায় হয়েছিলেন সুসংগঠিত। তাই বিজয়ের আনন্দ এতো অপ্রতিরোধ্য, এতো মধুর ও এত তৃপ্তির।
মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনগণকে যুদ্ধ করতে হয়েছিলো এক নির্মম শত্রুর বিরুদ্ধে, যারা চেয়েছিলো আমাদের নিশ্চিহ্ন করে শুধু পূর্ব বাংলার মাটিকে। চেয়েছিলো এই জনপদের জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে এই অঞ্চলকে পাকিস্তানের কলোনিরূপে ব্যবহার করতে। এখানকার মানুষকে দাবিয়ে রাখতে। দাবিয়ে রেখে আজীবন শোষণ করতে। একাত্তরের নয় মাসে পূর্ব বাংলায় যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারকীয় ধর্ষণ, লাখো মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন, লাখো মানুষকে ঘরবাড়ি ছাড়া করার ঘটনা ঘটে। তার উদ্দেশ্য ছিলো একটাই যাতে এখানকার মানুষ যেনো ভবিষ্যতে তার প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হতে না পারে। পাকিস্তানিদের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার স্পর্ধা দেখাতে না পারে। জেনারেল টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীদের উদ্দেশ্যই ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ চত্বরকে লাল রঙে রঞ্জিত করে তোলা। বাংলার মানুষের কন্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া। পূর্ব পাকিস্তানকে মৃত্যুপুরিতে পরিণত করা। সেই পরিকল্পনা মোতাবেকই তারা নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের হত্যা করার মহোৎসবে মেতে ওঠেন।
নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুনে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক অগ্নিবর্ষী বক্তব্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছিলেন, ‘আমরা লড়বো সমুদ্র তীরে। আমরা লড়বো শত্রুর অবতরণ ক্ষেত্রে। যুদ্ধ করবো আমরা মাঠে আর রাজপথে। আমরা যুদ্ধ করবো পাহাড়ে। কখনো আমরা আত্মসমর্পণ করবো না’। তার কিছুদিন পর ১৮ জুনে আরো জোরে সোরে তিনি পার্লামেন্টে বলেন, ‘আমরা প্রত্যেকটি গ্রামকে রক্ষা করবো। আমরা রক্ষা করবো প্রত্যেকটি শহরকে, নগরকে। বৃহত্তর পরিসরে লন্ডন নগরী যেখানে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হচ্ছে, অতি সহজে সমগ্র আক্রমণকারী বাহিনীকে গিলে খেতে পারে। আমরা কাপুরুষোচিত পন্থায় দাসত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে লন্ডন নগরীকে বরং যুদ্ধকালে বিধ্বস্ত এবং ভস্মিভূত এক জনপদ রূপে দেখতে চাই’। তার সেই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ জনগণ সীমাহীন সাহসিকতার সঙ্গে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তার সামনে নাৎসি বাহিনীর দুর্দমনীয় গতি স্তব্ধ হতে বাধ্য হয়।
মুক্তিযুদ্ধে অবশ্য আমাদের বীর যোদ্ধাদের সামনে এমন সাহসী উচ্চারণে কেউ কোনো বক্তব্য দেননি। মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ব্যতীত মুক্তিযোদ্ধারা শোনেনি রাজনৈতিক কোনো নেতার কোনো উজ্জীবনী বাণী, বক্তব্য বা বিবৃতি। মুক্তিযোদ্ধারা বরং নিজেদের সাহসে ভর করে এগিয়ে গেছেন, আর পৌঁছে গেছেন সেই ঐতিহাসিক গন্তব্যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সদর দরজায়। এই বিজয় যে কতো মহান, কতো বৈচিত্র্যময় তা পরিস্থিতির নিরিখেই শুধু অনুধাবন যোগ্য। অকাতরে প্রাণ দিয়ে, নির্বিচারে হাজারো বাঁকে বাঁকে রক্ত ঢেলে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অসম্ভবকে সম্ভব করে ইতিহাস গড়লেন। তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছালেন। এই অর্জনের কৃতিত্ব কেবল তাদের। এই অর্জন একক কোনো দলের, ব্যক্তির বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নয়। এই অর্জন জাতীয় অর্জন। জনগণের অর্জন। জনগণই এর রচয়িতা। জনগণই এর সংগঠক। জনগণের সীমাহীন ত্যাগই এর মূলধন। মুষ্টিমেয় রাজাকার, আলবদর ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে তাদের ত্যাগ স্বীকার করেন। অধিকাংশ পরিবারেই ১৬ ডিসেম্বর দেখা গেছে একদিকে যেমন বিজয়ের পরিতৃপ্তি, অন্যদিকে তেমনি সব হারানোর বুক ভরা ব্যথা।
কেউ হারিয়েছেন প্রিয় সন্তানকে, কেউবা পিতাকে। কোন মাতার কোল খালি হয়েছে। কোনো পিতার হৃদয় ভেঙেছে। কোনো ভাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে ধর্ষিতা বোনের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। কোনো পিতা সমগ্র পরিবারকে হারিয়ে হয়েছেন দিশেহারা। কোনো স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে হয়েছেন বিধবা। পুরো বাংলাদেশের চিত্রটাই তখন ছিলো এমন, সর্বত্রই প্রিয়জন হারানোর রোদন।
১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন পাঁচ সন্তান হারা মিসেস বিকসবির নিকট লিখিত চিঠিতে বলেছিলেন, আমি প্রার্থনা করছি, করুণাময় সৃষ্টিকর্তা আপনার (সন্তান হারানোর) যন্ত্রণা কিছুটা হলেও প্রশমন করবেন যেনো আপনার প্রিয়জনকে ভালোবাসা ও হারানোর বেদনা আপনার স্মৃতিতে অক্ষর হয়ে থাকে এবং স্বাধীনতার বেদীতে এই দুর্লভ আত্মত্যাগের গৌরববোধ আপনার একান্ত সম্পদ রূপে চিরস্থায়ী হয়’। অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হলো মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন বাংলাদেশে সেই স্বজন হারানোর আর্তনাদে কাতর মানুষদের নিকট ব্যক্তিগত পর্যায়ের হোক আর সামষ্টিক পর্যায়ে হোক এমন কোনো বক্তব্য নিয়ে কেউ তাদের কাছে উপস্থিত হননি। সেই ঐতিহাসিক অর্জনে গর্বিত জাতি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কোনোদিন ভোলেনি। জাতি তার গর্বিত সন্তানদের জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তানরূপে চিহ্নিত করেছে।
বাঙালি সংগ্রামী জাতি। সংকটকালে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সব বিভেদ ভুলে, দল মতের ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে, জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, এক কাতারে সম্মিলিত হয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এই দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রমাণ করেছিলেন, তারা স্বতন্ত্র। তারা অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য আলাদা। গন্তব্যও তাদের স্বতন্ত্র। একাত্তরের সেই সংকটময় মুহূর্তে যখন সবকিছু অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটায়।
মুক্তিযুদ্ধ জড়িয়ে আছে আমাদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে। এটি আমাদের আগামীর দিকে ধাবিত হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্ন বাস্তবায়নে উজ্জীবিত হতে শেখায়। আশাবাদী করে তোলে। এই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা ছিলো সব বৈষম্যের অবসান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন। শোষণহীন সমাজ গঠন। গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ। নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি নির্মূল করা। আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা প্রতিষ্ঠাসহ অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাস্তবায়ন, জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ়করণ।
স্বাধীনতার আজ ৫৪ বছর। বিগত ৫৩ বছরে জনগণ পেয়েছে গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরশাসন। নির্বাচনের নামে প্রহসন। জাতীয় ঐক্যের বদলে অনৈক্য ও বিভাজন, বিভাজনের রাজনীতির আস্ফালন। গত দেড় দশক ছিলো শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসন। যিনি গণতন্ত্র হরণ করে বিরোধী দল শূন্য রাজনীতির মঞ্চ বানিয়ে নিজেই সাজেন নিজের আলোচক, সমালোচক।
ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে চলছে দেশ। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের স্পিরিট ধারণ করে অন্তবর্তী সরকার সংবিধান, নির্বাচন, জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নিয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা, এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাগুলোর সঙ্গে জুলাই বিপ্লবের চেতনা যুক্ত করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান, আইন-কানুন প্রবর্তন করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশকে গণতন্ত্রের মহাসড়কে উঠিয়ে দেবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো ফ্যাসিবাদ তৈরি হতে না পারে।
লেখক: অধ্যাপক, ইউডা