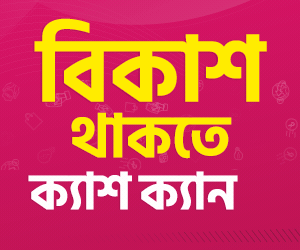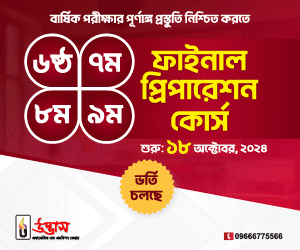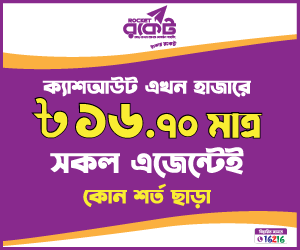আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নদীমাতৃক দেশ, যা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য পরিচিত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই দেশটি আজ কৃষি ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও নিম্নভূমির বৈশিষ্ট্য এটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি করে তুলেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই পরিবর্তনের প্রভাব কৃষি, অর্থনীতি, পরিবেশ এবং মানবিক অবস্থার ওপর ব্যাপকভাবে পড়ছে, যা দেশটির উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।
ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি জলবায়ু ঝুঁকিতে আছে, তার মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ দশে।
দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিত করে দীর্ঘমেয়াদে সমন্বিতভাবে ‘জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) গ্রহণ করেছিলো সরকার। ন্যাপে বলা হয়েছে, ওই ১৪টি জলবায়ু ঝুঁকি বা দুর্যোগের হার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঝুঁকিগুলোর তীব্রতা বাড়ছে বলেই আবহাওয়ার ধরনের পরিবর্তন এসেছে।
আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ধান, গম, সবজি এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এ ছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে গেছে, যা কৃষকদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের নদ-নদী ও জলাশয়গুলোর অবস্থাও সংকটাপন্ন। নদীভাঙন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং পানির স্তর হ্রাস পাওয়ার কারণে মৎস্য সম্পদও হুমকির মুখে পড়েছে। মাছ চাষ ও মৎস্য আহরণ দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে। এতে করে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাবে দেশের মানবিক অবস্থাও ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষদের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যার মতো দুর্যোগগুলো মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল এবং সম্পদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতে করে মানুষ তাদের জীবিকা হারাচ্ছে এবং দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। অনেক মানুষ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন করছে, যা শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। শহরগুলোর বস্তি এলাকায় বসবাসরত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যারা নিম্নমানের জীবনযাত্রা এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
জলবায়ু এ পরিবর্তনের প্রভাবে স্বাস্থ্যখাতে ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে পানিবাহিত রোগ যেমন ডায়রিয়া, কলেরা এবং টাইফয়েডের প্রকোপ বেড়ে গেছে। এ ছাড়া, উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার কারণে তাপজনিত রোগ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।
দেশের শিশু ও নারীদের ওপরও বিশেষ প্রভাব পড়ছে। দুর্যোগকালীন সময়ে শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। নারীরা নিরাপত্তাহীনতা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ ছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্পদের অভাব এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামাজিক অস্থিরতা এবং পারিবারিক সহিংসতার মতো সমস্যাগুলোকে ত্বরান্বিত করছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে বাংলাদেশের শিশুরাও রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন মারাত্মকভাবে জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে। তাদের মধ্যে ৫০ লাখ শিশুর বয়স পাঁচ বছরের কম; ১ কোটি ২০ লাখ শিশু বন্যাপ্রবণ এলাকার কাছাকাছি বাস করে এবং উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী ৪৫ লাখ শিশু তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ার ঝুঁকির মুখে রয়েছে।
ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (২০২১) অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা সবচেয়ে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ইন্টারন্যানাল ফুড পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউটের ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণগুলোর প্রভাবে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন ১০ শতাংশ কমে যেতে পারে। সমীক্ষায় আরো বলা হয়, উচ্চ তাপমাত্রা, বন্যা এবং অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দেশের গম উৎপাদন ৩০ শতাংশ, ভুট্টা ১৪ শতাংশ এবং আলুর উৎপাদন ৬ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।
কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব
ফসল উৎপাদন হ্রাস: বিশ্বব্যাংকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ৮ শতাংশ এবং গম উৎপাদন ৩২ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এ ছাড়া, অন্যান্য ফসল যেমন ভুট্টা, ডাল এবং সবজির উৎপাদনও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।
লবণাক্ততার প্রভাব: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বাড়বে। গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১৬-১৭ শতাংশ উপকূলীয় জমি লবণাক্ততার কারণে চাষের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে এই সমস্যা আরো প্রকট হবে।
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও খরা: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের ধরন অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। কিছু অঞ্চলে অতিবৃষ্টি এবং বন্যার পাশাপাশি অন্য অঞ্চলে খরার প্রবণতা বাড়বে। এই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ফসল চক্রকে ব্যাহত করবে এবং কৃষকদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।
ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ: তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং আর্দ্রতার পরিবর্তনের কারণে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়বে। এতে করে ফসলের উৎপাদন খরচ বাড়বে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে।
মানবিক বিপর্যয়
বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসন: বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১৩.৩ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, এবং তারা গ্রাম থেকে শহরে বা অন্য দেশে অভিবাসন করতে বাধ্য হবে। এই অভিবাসন শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।
দারিদ্র্য বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস এবং জীবিকা হারানোর কারণে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে, বিশেষ করে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে।
স্বাস্থ্যঝুঁকি: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়বে। উচ্চ তাপমাত্রা, বন্যা এবং পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে শিশু ও নারীরা স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হবে। গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে তাপজনিত রোগ, ডায়রিয়া, কলেরা এবং মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়বে।
খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা: কৃষি উৎপাদন হ্রাস এবং মৎস্য সম্পদ কমে যাওয়ার কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে। গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হতে পারে। বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই সমস্যা আরো তীব্র হবে।
অর্থনৈতিক প্রভাব
জিডিপি হ্রাস: বিশ্বব্যাংকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি ২-৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। কৃষি, মৎস্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অবকাঠামো ধ্বংস: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো অবকাঠামো ধ্বংস করবে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। এতে করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হবে।
পরিবেশগত প্রভাব
জলবায়ু উদ্বাস্তু: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের প্রায় ১০-১৮ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হতে পারে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের নদ-নদী ও জলাশয়গুলোর অবস্থাও সংকটাপন্ন হবে। নদীভাঙন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং পানির স্তর হ্রাস পাওয়ার কারণে মৎস্য সম্পদও হুমকির মুখে পড়বে।
সামাজিক প্রভাব
শিশু ও নারীদের ওপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শিশু ও নারীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে এবং নারীরা নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হবেন।
সামাজিক অস্থিরতা: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্পদের অভাব এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে, যা সামাজিক অস্থিরতা এবং পারিবারিক সহিংসতার মতো সমস্যাগুলোকে ত্বরান্বিত করবে।
ভৌগোলিক অবস্থান এবং নদীমাতৃক প্রকৃতির কারণে দেশটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ অংশ উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এই উপকূলীয় এলাকায় দেশের ১৯টি জেলা অবস্থিত, যা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত। এই অঞ্চলগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
চাষযোগ্য জমির পরিসংখ্যান
দেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ২.৮ মিলিয়ন হেক্টর (প্রায় ২৮ লাখ হেক্টর) উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত। এটি দেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৩০ শতাংশ অংশ। এই চাষযোগ্য জমিগুলো প্রধানত ধান, মাছ চাষ, সবজি এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই অঞ্চলের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।
উপকূলীয় এলাকার কৃষি ও চাষযোগ্য জমির চ্যালেঞ্জ
লবণাক্ততা: উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে চাষযোগ্য জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যায়, যা ফসল উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে।
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা উপকূলীয় এলাকার চাষযোগ্য জমিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১৬-১৭ শতাংশ উপকূলীয় জমি লবণাক্ততার কারণে চাষের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলীয় এলাকার কৃষি জমি এবং ফসল উৎপাদনকে ব্যাহত করে। এতে করে কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।
২০১১-১২ অর্থবছরের মোট বাজেটে কৃষি বাজেটের হিস্যা ছিলো ১০.৬৫ শতাংশ। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা নেমে এসেছে ৫ দশমিক ৯০ শতাংশে। একইভাবে কৃষি ভর্তুকির হিস্যা নেমে এসেছে ৬.৪ থেকে ২.৩ শতাংশে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে নির্ভর করতে হচ্ছে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থার ওপর,যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আমাদের বাজেটে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, কিন্তু কৃষি খাতে নেই। আমাদের অবস্থা নিধিরাম সর্দারের মতো।
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি দিন দিন বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার উপকুলবাসীকে বাচাতে হবে। তাদের মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে হবে। অন্তত তারা যেনো বাস্তুহারা না হয়।
সর্বোপরি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের দেশের কৃষি ও মানবিক বিপর্যয় একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সামগ্রিক ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা জরুরি। এ ছাড়া, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা এবং জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হতে পারে।
লেখক: বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত