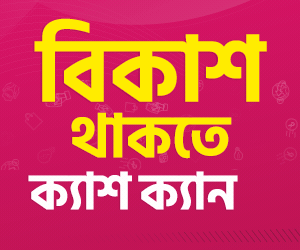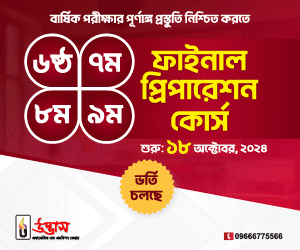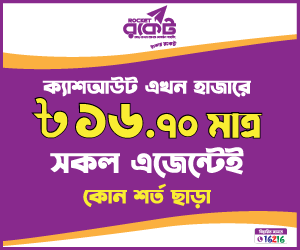বিশ্ববিদ্যালয় হলো দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্থান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেধাবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। কয়েক দশক আগেও দেশে এতো সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো না। এখন শহরের অভিজাত এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েক তলা ভবন নিয়ে দিব্বি চলছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি-এই কথাটা বলার জন্য হলেও গাঁটের টাকা খরচ করেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন অনেকেই। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের চোখ বুঁজে ধরে নেয়া হতো সর্বোচ্চ মেধাবী।
এখন আর তা হয় না। তার পেছনে অবশ্য নানা কারণ আছে। সেদিকে না যাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের মতো একটি ছোট দেশে ঠিক কতোটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার? এই যে এতো এতো বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে বা হচ্ছে আদৌ এতো দরকার আছে কি? এসবের মানের অবস্থা কী? গবেষণা চর্চায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার মান তো তলানিতে ঠেকছে।
বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা শোচনীয়। কয়েকটি র্যাঙ্কিংয়ের বিগত কয়েক বছরেরর ফলাফল অন্তত সেটাই বলে। তার মানে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সেই মান অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছি, যা একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকা দরকার। বিষয়টি আমরা স্বীকার করি আর নাই করি। এখন আবার সাত কলেজ নিয়ে একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন এবং তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। বাকিটা কর্তৃপক্ষের বিষয়। দেশের কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষাব্যবস্থা। অদৃশ্য অথচ দেশের স্থায়ী উন্নয়নে দরকার শিক্ষার। এখন প্রশ্ন হলো শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার মান অথবা রেজাল্ট! এখানে প্রশ্ন হলো কোয়ালিটি অথবা কোয়ান্টিটি। অর্থাৎ সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে, প্রচুর ভালো ফলাফল করছে তারপর চাকরির বাজারে এসে হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের তো দরকার কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা, প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় না। অলিতে-গলিতে যদি কিন্ডারগার্টেনের মতো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে তাহলেই শিক্ষা অনেক এগিয়ে গেলো এটা ভেবে নেয়ার কোনো কারণ নেই। সারা বিশ্বে কয়েক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যা অনুপাতে এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে আসলে কতোটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার সেই পরিমাপ করা দরকার। তবে কার্যকর কোনো পদ্ধতি নেই। কারণ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এসব কোথায় কীভাবে কতোটি দরকার তা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। যদিও এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেই, তবে কতোটা বৃদ্ধি প্রয়োজন সেটাও ভাবা দরকার।
২০০৫ থেকে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর সময়কে ‘জাতিসংঘ শিক্ষা দশক’ হিসেবে গণ্য করে ইউনেসকো গুণগত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপাদান ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। এ সংস্থাটি গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেছে। দৃশ্যটা যদি এমন হয় তাহলে কোয়ালিটি এডুকেশন প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং এই শিক্ষা কোনো দেশের কাম্য শিক্ষা হতে পারে না। এই শিক্ষা দেশকে এক গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যায়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করলাম, আমরা পাসের হার বাড়ালাম সেই সঙ্গে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তৈরি করলাম! এমনটা হলে তো দেশ থমকে যাবে। আমাদের শিক্ষা কাঠামো প্রশ্নবিদ্ধ হবে বা ইতোমধ্যেই হয়েছে। সেখান থেকে বেড়িয়ে আসাতে হবে। বহু বছর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পাসের হার বৃদ্ধি এবং তার থেকেও ভালো ফলাফলের দিকে, যা এক শ্রেণির নেতিবাচক অবস্থা তৈরি করেছে। শিক্ষার ওপর থেকে আস্থা উঠে যাচ্ছে। এর মানে হলো আমরা ক্রিম স্টুডেন্ট বলতে যা বোঝাতে চাই সেই ধরনের ছাত্রছাত্রী বের করতে পারছি না। গত বছরের একটি তথ্যে-উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন দেশে বেশি, তার একটি তালিকা প্রকাশ করে ডেইলিওডটইন নামের একটি ওয়েবসাইট। তাদের করা তালিকা অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে। এ ছাড়া সবচেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকার দেশগুলোর মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ।
ভারতে ৫ হাজার ২৮৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৩ হাজার ২১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্দোনেশিয়ায় মোট ২ হাজার ৫৯৫টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। চীনে ২ হাজার ৫৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ব্রাজিলে আছে ১ হাজার ২৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। আসলে কোন দেশে কতোটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা উচিত সেটা নির্ণয় করা খুব জটিল একটি প্রক্রিয়া। তবে এটা জটিল না। যে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃতই উচ্চশিক্ষার কাজটি যথাযথভাবে করছে কি না। আপনি দেশের সার্বিক বেকারত্বের দিকে তাকান, আপনি দেশের মোরালিটির দিকে তাকান। এতো এতো উচ্চশিক্ষিত মানুষ, অথচ আমরা বৈশ্বিকভাবে বহু ক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের যেখানে উন্নতি দরকার বা যে ধরনের মানব সম্পদ প্রয়োজন সে আমরা বের করতে পারছি না। আরো বিশ্ববিদ্যালয় হতেই পারে বা হবে এটাই স্বাভাবিক ধরলাম কিন্তু তাতে কি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার নিশ্চয়তা দিতে পারছি বা পারবো? যদি সেটা না পারা যায়, তাহলে এতো বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে হবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় মানে উচ্চশিক্ষা। এখন প্রশ্ন হলো সবার জন্যই কি এটা দরকার আছে বা রাষ্ট্রের এতো সংখ্যক মাস্টার্স পাস বেকার দরকার আছে? দক্ষতার প্রশ্নে এখানে আমরা ছাড় কেনো দিচ্ছি? যেখানে উন্নত বিশ্বে দরকার প্রচুর দক্ষ কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ, সেখানে একটি বড় অংশই তেমন কোনো দক্ষতা নিয়ে বড় হচ্ছে না। অথচ চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রযুক্তি সম্পন্ন বিশেষত বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন করে তৈরি করছে। দেশের বাজারেই চাকরিতে হিমশিম খাচ্ছে লাখ লাখ তরুণ-তরুণী। আমরা বিদেশে পাঠাচ্ছি শ্রমিক।
যদি দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী পাঠাতে পারতাম তাহলে আরো বেশি কাজে আসতো। খোদ চীনেই কিন্তু উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছে তরুণরা। গণমাধ্যমের খবর এমনটাই। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উচ্চতর ডিগ্রির কার্যকারিতা কমে যাওয়াই মূলত উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার মূল কারণ। উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের কলেজগুলোতেও চালু করা হয়েছে অনার্স কোর্স। সেসব কোর্সের মানসম্মত শিক্ষক আছে কি নেই বা পর্যাপ্ত শিক্ষক আছে কি না সে খোঁজ আর রাখা হচ্ছে না। কিন্তু সেখানেও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে। সকলেই অনার্স-মাস্টার্স করছে। এটা সবার অধিকার। কিন্তু এরপর? এরপরেই তো তারা নামছে চাকরির বাজারে। সেখানেই একরাশ হাতাশা এবং বিরক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে। কোনো রকম দক্ষতা ছাড়াই একটি বড় অংশ চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে। আমাদের গত এক দশকে কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক গতি আনা প্রয়োজন ছিলো। সে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজন ছিলো গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। সেটাও প্রায় অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লে তো সমস্যা নেই যদি মান ঠিক রাখা যায়। কিন্তু এভাবে কতো বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার আমাদের আছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য তো শেখা। যদি সেটা না হয় তাহলে আর পড়ালেখা করে লাভ কী? তবে উচ্চশিক্ষায় যে গবেষণা, চর্চা ও প্রজ্ঞা দরকার সেটা খুব বেশি অর্জন করা যাচ্ছে না। গত এক দশকে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়েছে। আর গত কয়েক বছরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার উদ্দেশ্য হলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী করে তোলা। শিক্ষার এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এসডিজি অর্জনের জন্য মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। নামে মাত্র পাশ আর ডিগ্রি সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষিত বেকার তৈরি হয় শিক্ষিত জাতি নয়। তাই এই বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার চাহিদার পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমান যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগ তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্র বলছে দক্ষতা থাকলে চাকরি হবেই আর তারা বলছেন মাস্টার্স করার পরও কেনো বেকার থাকতে হচ্ছে।
লেখক: শিক্ষক