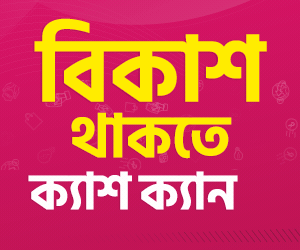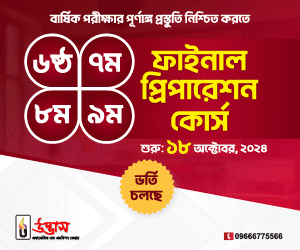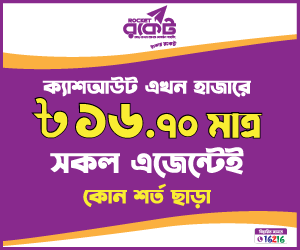বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব সন্জীদা খাতুন একাধারে রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক, সংগীতজ্ঞ ও শিক্ষক । ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে তিনি। কবি শঙ্খ ঘোষ একবার তার সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘গান তার জীবিকা নয়, গান তার জীবন, চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে মিশে যাওয়া এক জীবন। একুশে ভাষা এসেছিলো তার মননে, একাত্তরে সুরের আগুন কণ্ঠে উঠেছিলো তার দীপ্ত জয়োল্লাসে।
বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সর্বতোভাবে জড়িয়ে থেকে বহু মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন বড় আপনজন। পরিচিতি পেয়েছেন ছায়ানটের ‘মিনু আপা’ থেকে শান্তিনিকেতনের ‘মিনুদি’ হিসেবে। সাতচল্লিশের দেশভাগ, দাঙ্গা ও রক্তপাতের সাক্ষী বাঙালির সাহসী সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার অবিসংবাদী নারী সন্জীদা খাতুন। অশুভ ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন শুভ ও কল্যাণের কথা অকুতোভয়ে। সংস্কৃতিকে সঙ্গী করে দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন সম্প্রীতির পথে আলোর সন্ধানে । সুরকে হাতিয়ার করে লড়াই করেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, অপশক্তির বিরুদ্ধে।
সম্প্রীতি ও প্রগতির দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কেটে যায় যার প্রতিটি দিনরাত তিনি হলেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের সভাপতি ড. সন্জীদা খাতুন।
তার ৮৫তম জন্মদিনের আগের দিন বিকেলে ছায়ানট ভবনে আপন অনুভূতি ব্যক্ত করেন সন্জীদা খাতুন। সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে আসে আপন ভাবনার কথা। জন্মদিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জন্মদিন উদযাপন প্রসঙ্গে আমার নিজের কোনো আগ্রহ নেই। আমার কাছে মানুষের জন্মদিনকে একটি জৈবিক ব্যাপার মনে হয়। তাই আমার কাছে জন্মদিনের অর্থ হচ্ছে বেশি বুড়ো হয়ে যাওয়া। আর আমার জন্মদিনের চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এ বছর রমনা বটমূলের বর্ষবরণের আয়োজনটি পদার্পণ করবে ৫০ বছরে।
আমি সারাটি জীবন সংস্কৃতির শুদ্ধতাকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ, সংস্কৃতি মানুষের মনকে সুন্দর করে তোলে। তাই নিজে মঞ্চে উঠে গান গাওয়ার পরিবর্তে সংগঠকের ভূমিকাকেই বড় করে দেখেছি। প্রতিদানে কিছুই চাইনি। সবসময় সংস্কৃতির আলোয় মানুষের মনের কথাটি বলতে চেয়েছি। মুসলমানিত্বের চেয়ে বাঙালিত্বের গৌরববোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। মানুষের মানবিক হয়ে ওঠাকে গুরুত্ব দিয়েছি। জাতীয় অধ্যাপক ও লেখক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের মেয়ে সনজীদা খাতুন। এর বাইরে তিনি খ্যাতিমান লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের বোন এবং রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওয়াহিদুল হকের স্ত্রী। তিনি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন।
১৯৭৮ খ্রিষ্টাবেদ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ’ গবেষণাপত্রে পিএইচডি লাভ করেন। সনজীদা খাতুনের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষক হিসেবে। শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতকোত্তর লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি সর্বদাই প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাঙালিত্বের বোধ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছেন।
নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটল এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আলোয় পৃথিবীর মুখ দেখার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছেন । কর্মময় জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ সনজীদা খাতুন অর্জন করেছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের স্বর্ণপদক ও সম্মাননা, সা’দত আলী আখন্দ পুরস্কার, অনন্যা পুরস্কার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানজনক ফেলোশিপ, বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা স্বীকৃতি। তার কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে ওপার বাংলাতেও। তার কর্মময়তার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সনজীদা খাতুনকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান ‘দেশিকোত্তম’ প্রদান করেছে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ‘রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার’, কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধি। জীবনভর অশুভের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন কল্যাণের কথা। বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলো রবীন্দ্র সংগীত৷ আর সে বাধা ভেঙেছিলেন যারা, সনজীদা খাতুন তাদের অন্যতম৷ রবীন্দ্রনাথের গান এখন আর রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক নয়৷ অথচ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের ওপর তোলা হয়েছিরো নিষেধের বেড়া৷ সেই বেড়া ভাঙতে সক্রিয় ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগীরা৷
স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংগীত চর্চার প্রাথমিক পর্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হবার পর প্রখ্যাত সংগীতকার আব্দুল আহাদ ঢাকায় আসেন৷ তিনি তো শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত৷ তিনি এসে রেডিওতে কাজ আরম্ভ করেন৷ রেডিওতে উনি রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন৷ অতি সুন্দর করে ভাব বিশ্লেষণ করে শেখাতেন৷ আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে গান শিখতাম৷ তা ছাড়া আব্দুল আহাদ যখনই রবীন্দ্র জন্মবর্ষে বা মৃত্যুদিনে অনুষ্ঠান করতেন, যারা ঢাকায় রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন তাদের সবাইকে ডেকে খুব সুন্দর করে অনুষ্ঠানগুলো করতেন। উনি রেডিওতে যে মান বজায় রেখেছিলেন সেটা ছিলো খুবই ভালো৷ কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা সময় এলো যখন আমরা দেখতে পেলাম পাকিস্তান সরকার ঠিক চাইছেনা যে রবীন্দ্র সংগীত এখানে প্রচার হোক৷ রেডিওতে শুধু না, বাইরেও গাওয়া হোক এটা তারা চাইছিলো না৷ কিন্তু সেটা যে তারা খুব স্পষ্ট করে বলতো এমনও নয়৷ কিন্তু বুঝতে পারতাম যে মানুষের মধ্যেও একটা অন্য চাহিদা এসেছিলো৷ বড় জোর গিটারে রবীন্দ্রসংগীত বাজালে লোকে শুনতো৷ কিন্তু আমাদের গান গাইবার সুযোগ খুব একটা মিলতো না৷
প্রয়াত কাজি মোতাহার হোসেন ছিলেন অত্যন্ত উদার স্বভাবের এবং রবীন্দ্রভক্ত৷ ফলে বাবার কাছ থেকে উৎসাহের অভাব ছিলো না কন্যা সনজীদার জন্য৷ রবীন্দ্র সংগীত শিখেছেন, গেয়েছেন৷ পরবর্তীকালে শিখিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন ‘ছায়ানট' প্রতিষ্ঠান৷ অল্প বয়স থেকেই অনুষ্ঠানে গান করেছেন সনজীদা৷ পঞ্চাশ দশকের একটি অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করলেন তিনি বিশেষভাবে-- ‘পঞ্চাশ দশকে একবার-আমার খুব ভালো করে মনে আছে-কার্জন হলে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিলো৷ আমাকে গান গাইতে বলা হয়েছিলো৷ আমি খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম গান গাইতে৷ কী গান গাইবো? এমন সময় দেখা গেলো সেখানে বঙ্গবন্ধু৷ তখন তো তাকে কেউ বঙ্গবন্ধু বলে না-শেখ মুজিবুর রহমান৷ তিনি লোক দিয়ে আমাকে বলে পাঠালেন আমি যেনো ‘সোনার বাংলা’ গানটা গাই -‘আমার সোনার বাংলা’৷ আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম৷ এতো লম্বা একটা গান৷ তখন তো আর এটা জাতীয় সংগীত নয়৷ পুরো গানটা আমি কেমন করে শোনাবো? আমি তখন চেষ্টা করে গীতবিতান সংগ্রহ করে সে গান গেয়েছিলাম কোনোমতে৷ জানি না কতোটা শুদ্ধ গেয়েছিলাম৷
কিন্তু তিনি এইভাবে গান শুনতে চাওয়ার একটা কারণ ছিলো৷ তিনি যে অনুষ্ঠান করছিলেন, সেখানে পাকিস্তানিরাও ছিলো৷ তিনি দেখাতে চেষ্টা করছিলেন তাদেরকে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ কথাটা আমরা কতো সুন্দর করে উচ্চারণ করি৷ এই সমস্ত গানটার ভেতরে যে অনুভূতি সেটা তিনি তাদের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছিলেন৷ আমার তো মনে হয় তখনই তার মনে বোধহয় এটাকে জাতীয় সংগীত করবার কথা মনে এসেছিলো৷ বায়ান্ন খ্রিষ্টাব্দে যখন আমরা রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করি তখন আমরা কিন্তু ওই বায়ান্নর পরে পরে শহীদ মিনারে প্রভাতফেরিতে রবীন্দ্র সংগীত গাইতাম৷ এইভাবে রবীন্দ্র সংগীত কিন্তু তখন বেশ চলেছে৷ আরো পরে কেমন যেনো একটা অলিখিত বাধা এলো৷ পাকিস্তান আমলের পরে রবীন্দ্রসংগীত ‘আমার সোনার বাংলা' যখন জাতীয় সংগীত হলো, তার কিছুকাল পরে দেখা গেলো-নানা ধরনের ওঠাপড়া চলছিরো, তো সেই সময় গানটা না করে শুধু বাজনা বাজাবার একটা রেওয়াজ শুরু হলো৷ আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই পাকিস্তানি মনোভাবটা কাজ করেছে৷’ সনজীদা খাতুনের ভাষায়, ‘১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে যখন রবীন্দ্র শতবর্ষ হলো, ততোদিনে আমি সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা৷ কাজেই আমার পক্ষে গান গাওয়া খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিলো বাইরের অনুষ্ঠানে৷ রেডিওতে গাইতাম৷ শতবর্ষ উপলক্ষে ‘তাসের দেশ’ নাটক করা হচ্ছিলো মঞ্চে৷ গান গাইতে হবে৷
 আমি গান গাইতে বসে গেলাম৷ কিন্তু মুখের মধ্যে একটা রুমাল পুরে দিয়ে আমি গান গেয়েছিলাম৷ কারণ, আমার গলা চিনে ফেললে আমার সরকারি চাকরিতে অসুবিধা ছিলো৷ এই অনুষ্ঠানে গানটা গেয়ে আমি বেরিয়ে আসছি, আহাদ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘কে গাইলো বলতো? ভালই তো লাগলো৷’ আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলাম সামনে থেকে৷ কারণ, আমি গেয়েছি এটা যদি প্রচার হয়ে যায় তাহলে আমার চাকরিতে অসুবিধে হবে৷ এইসব দিন তখন আমরা পার করেছি৷ তিনি মোট ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ, ধ্বনি থেকে কবিতা, অতীত দিনের স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ: বিবিধ সন্ধান, ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা, স্বাধীনতার অভিযাত্রা সাহিত্য কথা সংস্কৃতি কথা, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ও জননী জন্মভূমি।[inside-ad-2]
আমি গান গাইতে বসে গেলাম৷ কিন্তু মুখের মধ্যে একটা রুমাল পুরে দিয়ে আমি গান গেয়েছিলাম৷ কারণ, আমার গলা চিনে ফেললে আমার সরকারি চাকরিতে অসুবিধা ছিলো৷ এই অনুষ্ঠানে গানটা গেয়ে আমি বেরিয়ে আসছি, আহাদ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘কে গাইলো বলতো? ভালই তো লাগলো৷’ আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলাম সামনে থেকে৷ কারণ, আমি গেয়েছি এটা যদি প্রচার হয়ে যায় তাহলে আমার চাকরিতে অসুবিধে হবে৷ এইসব দিন তখন আমরা পার করেছি৷ তিনি মোট ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ, ধ্বনি থেকে কবিতা, অতীত দিনের স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ: বিবিধ সন্ধান, ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা, স্বাধীনতার অভিযাত্রা সাহিত্য কথা সংস্কৃতি কথা, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ও জননী জন্মভূমি।[inside-ad-2]
শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। মুকুল ফৌজে কাজ করেছেন, আবার ছেড়েও দিয়েছেন। তার প্রথম গানের গুরু ছিলেন সোহরাব হোসেন। তার কাছে তিনি শিখেছিলেন নজরুলসংগীত, আধুনিক বাংলা গান এবং পল্লিগীতি। পরে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন হুসনে বানু খানমের কাছে। পরে আরো অনেকের কাছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, আবদুল আহাদ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনসহ কয়েকজন। হৃদয়মথিত সুরের মূর্ছনায় যিনি নিজেকে সঁপেছিলেন রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় তিনি সনজীদা খাতুন। বাংলাদেশের এক বর্ণাঢ্য ও অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।
সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি শুদ্ধতার প্রতীক। মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত তৈরিতে যে ছায়ানট অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলো তিনি তার সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তিনিকেতনের উচ্চশিক্ষাই শুধু নয়, স্বশিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির নিমগ্নচর্চায় সনজীদা খাতুন নিজেই এখন একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাংস্কৃতিক যোদ্ধা ড. সনজীদা খাতুন।
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক