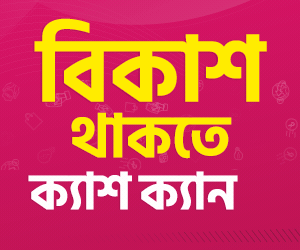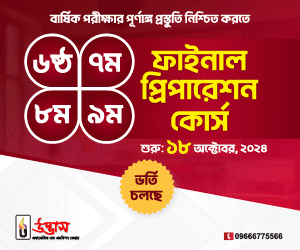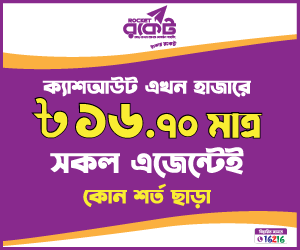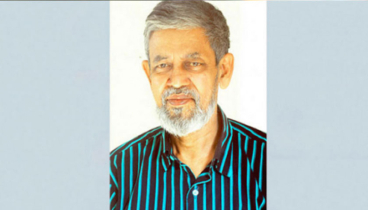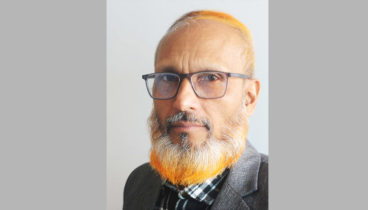গত ৪ এপ্রিল থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ৩ এপ্রিল ২০তম বিমসটেকের মন্ত্রীপর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করেন। গত ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা ‘বিমসটেক ইয়াং জেনারেশন ফোরাম: হোয়ার দ্য ফিউচার মিটস’ শীর্ষক ফোরামে কি-নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্যও দেন।
বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশে এই অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রথম ধারণাটি আসে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর মূল উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে থাইল্যান্ড। তারা এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে এবং বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যোগাযোগ করে।
দেশগুলো নীতিগতভাবে সম্মতি জানায় এবং জোটে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ‘ব্যাংকক ঘোষণার’ মাধ্যমে বিমসটেক তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর মিয়ানমারের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে সংস্থার নামের সঙ্গে ‘এম’ যুক্ত হয়।
২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জুলাই ভুটান, ও নেপালের সংযুক্তির মাধ্যমে এর সদস্য সংখ্যা সাতে উন্নীত হয় এবং নামকরণ করা হয় ‘বে অব বেঙ্গল ইনসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)।
আঞ্চলিক এই সংস্থাটির প্রধান সাতটি সহযোগিতার খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন--বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শক্তি, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জনগণের মধ্যে সংযোগ ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন।
গত ১২ মার্চ বিমসটেকের ঢাকা কার্যালয়ে ‘দ্য নিই ওয়ার্ল্ড অর্ডার, গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড বিমসটেক’ শীর্ষক উপস্থাপনা পেশ করেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিংয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান।
তার গবেষণায় সংস্থাটির যে চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে বলা হয়, তার মধ্যে ছিলো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ঘাটতি, সদস্যদেশগুলোর স্থায়ী প্রতিশ্রুতির অভাব, সনদ গ্রহণে দীর্ঘ বিলম্বের ফলে সীমিত প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, স্বল্প আঞ্চলিক বাণিজ্য, অবকাঠামোগত ঘাটতি, সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন, যেমন বাংলাদেশ-মিয়নামার, সম্পদের সীমাবদ্ধতা বা অপর্যাপ্ত তহবিলপ্রাপ্ত সচিবালয় ও দক্ষ জনবলের অভাব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গত ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিমসটেক সম্মেলন শীর্ষক ব্রিফিং।
সেখানে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে এবারের ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন নতুন বাংলাদেশের জন্য বিমসটেকের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক অঙ্গনে নতুন পদচারণা। এবারের সম্মেলন আমাদের জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশকে উপস্থাপনের সুযোগ এনে দেবে। বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিমসটেক সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় ও গভীর করবে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’ ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ দুই বছরের জন্য বিমসটেকের সভাপতিত্ব গ্রহণ করার মধ্যে আলাদা এক গুরুত্ব পেয়েছে এই সম্মেলন।
বিমসটেকের সম্ভাবনা অনেক। বাণিজ্য সহযোগিতা বাড়ানো, বিনিয়োগ এক দেশ থেকে আরেক দেশে নেয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি স্থাপন করা। তবে, পরিবেশ, ব্লু ইকোনমি ও ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বাস্তবায়নের রাজনৈতিক সিগন্যাল না পাওয়ায় এগুলো এগুতে পারছে না। সার্ক যেমন ভারত দ্বারা প্রভাবিত, বিমসটেকও তাই। বিমসটেকের দাপ্তরিক ব্যয়ের ৩২ শতাংশ বহন করে ভারত, যদিও এর প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে।
বিমসটেকের কার্যকারিতা নিয়ে নিজেকে অত্যন্ত আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী উল্লেখ করেন এর মহাসচিব ইন্দ্র মনি। তবে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের মধ্যে পরিকল্পনাগুলোর নীতিগত দিক নিয়ে মতানৈক্যও রয়েছে। তাই বিশ্লেষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এ জোটও সার্কের মতো পথ হারায় কি না। বিমসটেকের দুই সদস্যদেশ মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড আসিয়ানেরও সদস্য। অতএব, দক্ষিণ এশিয়া ও আসিয়ানের মধ্যে একটা মেলবন্ধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো গভীর করার একটা লক্ষ্য ছিলো বিমসটেক প্রতিষ্ঠার সময়। সেটি কতোটা এগোলো প্রশ্ন বিশ্লেষকদের।
বিমসটেক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। এ চুক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও এখনো চূড়ান্ত ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হয়নি। এ ছাড়া বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেমন-পরিবহন সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনা।
এর মাধ্যমে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও বিনিয়োগের একটা ত্রৈমাত্রিক সংশ্লেষ করার সুযোগ ছিলো বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এই উদ্দেশে ‘এমিন্যান্ট পারসনস গ্রুপ’ গঠন করা হয়েছিলো। তাদের প্রতিবেদন নিয়ে এই সামিটে আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু ২৮ বছরে বিমসটেকের যে গতিতে অগ্রসর হওয়ার আশা ছিলো, সংস্থাটি তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। এর কারণ কী?
বিমসটেক, সার্ক ও আসিয়ানের মতো রিজিওনাল তথা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সাধারণত রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এর নেতৃত্বে এবং নীতি নির্ধারণীতে থাকেন রাজনীতিবিদরা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের এসব সংস্থায় নেতৃত্ব দেয়ার মতো, এগুলোর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা এবং সত্যিকার অর্থে জনবান্ধব বা সদস্যদেশগুলোর জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য করা তাদের ধাতে থাকে না, তাদের সে ধরনের উদারতা, মেধা, অভিজ্ঞতা থাকেনা। ফলে এসব সংস্থাগুলো আর সামনে আগাতে পারে না। যেমন সার্কের সদস্য পাকিস্তান ও ভারত--যে দেশদুটি সীমিত স্বার্থের বাইরে যেতে পারে না।
দেশদুটো তাদের জনগণের এবং অর্থনীতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কিছু করা চিন্তা করতে পারে না। তারা চিন্তা করে একে অপরের বৈরিতা দিয়ে। একইভাবে, সার্কের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হওয়ায় পুর্ববর্তী সরকারও সার্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর সামনে এগোয়নি।
সাম্প্রতিকালে ভারত যে বাংলাদেশি জনগণের জন্য টুরিস্ট ভিসা বন্ধ রেখেছে সেও ওই একই সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে। ভারতের জনগণ ও ব্যবসায়ীরা এতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সরকারের কিছুই আসে যায় না। এভাবেই রাজনীতিবিদদের কব্জায় থাকা সংস্থাগুলো সামনে আগাতে পারে না, জনগণের প্রকৃত কল্যাণে তেমন একটা কিছু করতে পারে না শুধুমাত্র কিছু আনুষ্ঠানিকতা ও কাগুজে প্রতিশ্রুতি দেয়া ছাড়া।
দেশের বিশ্ববিদ্যালয় নেতা সৃষ্টির একটি উত্তম জায়গা। সেই চর্চা কয়েক যুগ আগেই আমাদের দেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় নেতা সৃষ্টি না করে সৃষ্টি করছে মাস্তান, দুর্বৃত্ত, চাঁদাবাজ আর চাকরিপ্রার্থী। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো ঘটনাও নেতা সৃষ্টি করে। নেতৃত্বের যে স্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সেই স্ফুলিঙ্গ কোনো বিশেষ ঘটনা, সময় ও পরিবেশে আগ্নেয়গিরির মতো বের হয়।
তখন জাতি ও পৃথিবী তাদের চিনতে পারে। তাদের পতাকাতলে সমবেত হয় মানুষ। সেই চর্চাও আমাদের দেশে কয়েক যুগ একেবারেই বন্ধ ছিলো। কারণ, রাজনীতিবিদেরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে ভয় পায়, তারা জ্বালামুখ সব সময় বন্ধ রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারপরেও বিকল্প পথে সেই অগ্ন্যুৎপাত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত বছর।
সেই পরিবর্তনের কারণেই এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ফোরামে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব গ্রহণ বিশাল ব্যাপার যা পরিমাপ করা আমাদের দেশের কিংবা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশের মূল্যায়ণ করার অবস্থা নেই। কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব বা দল কোনোসময়ই চাইবে না, চায়না এ ধরনের লোক নেতৃত্বে আসুক। কারণ, তারা চায় নিজেদের স্বার্থ, পার্টির লোকজনের স্বার্থ। সেটি করতে গিয়ে দেশ গোল্লায় গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না।
তারা বরং এসব আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কথা ও কাজে ভুল ধরার জন্য বসে থাকে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস যেসব পদক্ষেপ নিতে পারবেন, নেবেন সেগুলো এ ধরনের একটি সংস্থাকে প্রকৃত অর্থেই জনগণের কল্যাণে, সদস্যদেশগুলোর কল্যাণে পরিচালিত হবে। কিন্তু এসব ব্যক্তিত্বকে সেই রাজনৈতিক মোসাহেবরা সরাতেই ব্যস্ত থাকবেন, এটিই মানব সভ্যতার ইতিহাস।
এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে দেশে ফেরতের উপযুক্ত হিসেবে তালিকভুক্ত করেছে মিয়ানমার। এর ক্রেডিট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। তিনি বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাকটিক্যালি যেভাবে নাড়াচাড়া দিয়েছেন সেটি পূর্ববর্তী সরকার একমাত্র মৌখিক আর কাগুজে কিছু কাজ ছাড়া করতে পারতো না।
বিমসটেকের শীর্ষ সম্মেলনের ভেন্যু সাংগ্রিলা হোটেলেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ৪০ মিনিটের বৈঠক হয়েছে আমাদের প্রধান উপদেষ্টার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে আলোচনায় না বসার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিত্বের কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে। আলোচনায় যাই হোক, অন্তত এতো বড় এই প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক সেটির বরফ অন্তত কিছুটা হলেও গলবে।
এই দুই দেশের জনগণ সুসম্পর্কের কারণে অনেক উপকৃত হতে পারতো কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতা যা রাজনীতিবিদেরা নিজেদের স্বার্থে জিইয়ে রাখেন সেজন্য সম্ভব হয় না অনেক কিছু। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সেখানে তারা তাদের চুরি যাওয়া অর্থ উদ্ধারে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকটা কার্যকরী হতো পারে। তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।
এসব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে কার্যকরীভাবে কথা বলার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা বা যোগ্যতা কোনটাই থাকে না (অনন্য ব্যতিক্রম ছাড়া)। যেসব কথা তারা এসব ফোরামে বলেন সেগুলো তারা যে বিশাল বাহিনী নিয়ে যান তাদের কাছ থেকে নেয়া দুচারটে গৎবাঁধা লিখিত কথা উপস্থাপন করেন, যার কোনো ইফেক্ট কখনো থাকে না।
এসব মোসাহেব, চাটুকার ও প্রজ্ঞাহীন রাজনীতির অনুসারীরা নেতাকে ‘জিরোকে হিরো’ বানান এবং যুক্তিহীন বা কোনো ধরনের ফলপ্রসূ না আলোচনাকে বিরাটভাবে ম্যাগনিফাই করেন। ফলে, এসব সংস্থা সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এগোতে পারে না।
রাজনীতিবিদদের গ্লোরিফাই করা, প্রশংসায় ভাসিয়ে দেয়া, মাথার মুকুট হিসেবে রাখা-একটি দেশের অভ্যন্তরীণ জনগণ করতে পারে কিন্তু এগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি, প্রজ্ঞা, যুক্তি কোনোটিই যায় না। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর একই অবস্থা। বাংলাদেশে তো সেখানে চ্যাম্পিয়ন। সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ অন্তত একটা দিশা পেতে যাচ্ছে বলে মনে হয় কিন্তু রাজনীতিবিদদের আলোচনা, সমালোচনা ও ভীতিপ্রদর্শন দেশ এবং দেশ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কতোটা ফায়দা এনে দেবে সেটিই দেখার বিষয়।
লেখক: ক্যাডেট কলেজের সাবেক শিক্ষক